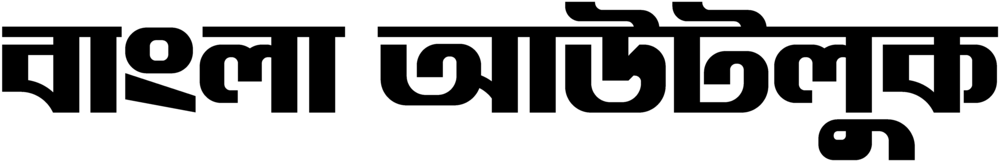আল জাজিরার প্রতিবেদন
চীনের বিরুদ্ধে পশ্চিমের যুদ্ধোন্মত্ততার আসল কারণ
ডিলান সালিভান
প্রকাশ: ০৪ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৮ এএম

শাংহাই, চীনের অ্যাগিবট কারখানায় মানবসদৃশ রোবটের অ্যাসেম্বলি লাইনে কাজ করছেন কর্মীরা, ২০ মার্চ ২০২৫ \[ফাইল ছবি: ফ্লোরেন্স লো/রয়টার্স]
গত দুই দশকে চীনের প্রতি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক সহযোগিতা থেকে শত্রুতার দিকে মোড় নিয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যম ও রাজনীতিকেরা চীনের বিরুদ্ধে একটানা নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার চীনের ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, সামরিক উপস্থিতিও জোরদার করেছে চীনের সীমানার আশপাশে। ওয়াশিংটন চেষ্টা করছে বিশ্বকে বোঝাতে যে চীন বিপজ্জনক।
চীনের উত্থান আসলে মার্কিন স্বার্থের জন্য হুমকি ঠিকই, তবে সেই হুমকি যেভাবে মার্কিন রাজনৈতিক নেতারা তুলে ধরেন তা প্রকৃত চিত্র নয়।
চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে বুঝতে হলে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। বৈশ্বিক পুঁজির কেন্দ্রে থাকা উত্তরাংশের দেশগুলো দক্ষিণাংশের দেশগুলো থেকে সস্তা শ্রম ও সস্তা কাঁচামাল নিয়ে উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করে। বৈশ্বিক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর চেইন এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে চলে। উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পণ্যের দামের ব্যবধানের কারণেই কেন্দ্রীয় দেশগুলো প্রান্তিক দেশগুলোর কাছ থেকে বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যের অতিরিক্ত আহরণ করতে পারে।
১৯৮০’র দশকে চীন যখন পশ্চিমা পুঁজির জন্য দরজা খুলে দেয়, তখন থেকে দেশটি এই ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। অ্যাপল কোম্পানির অনেক উৎপাদনই চীনা শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। অর্থনীতিবিদ ডোনাল্ড ক্লেল্যান্ডের গবেষণা বলছে, যদি অ্যাপল কোম্পানিকে চীনের শ্রমিকদের আমেরিকানদের মতো মজুরি দিতে হতো, তাহলে একটি আইপ্যাডের জন্য বাড়তি ৫৭২ ডলার খরচ হতো।
কিন্তু গত বিশ বছরে চীনে শ্রমিকদের মজুরি অনেক বেড়েছে। ২০০৫ সালের দিকে চীনে প্রতি ঘণ্টায় শ্রমিক খরচ ছিল এক ডলারের নিচে, এখন তা আট ডলারের বেশি। ভারতে এখনও তা দুই ডলারের কাছাকাছি। চীন বর্তমানে এশিয়ার যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে উচ্চ মজুরি দিচ্ছে।
এর পেছনে কয়েকটি বড় কারণ রয়েছে। চীনে অতিরিক্ত শ্রম ধীরে ধীরে বেতনভিত্তিক শ্রমবাজারে মিশে গেছে, এতে শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও বড় হয়েছে। সরকারি চিকিৎসা, সরকারি আবাসন ব্যবস্থা – এসবের সম্প্রসারণে শ্রমজীবীদের অবস্থা উন্নত হয়েছে।
এই উন্নয়ন চীনা শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক হলেও পশ্চিমা পুঁজির জন্য তা সমস্যার। চীনে বাড়তি মজুরি পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর লাভের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু, এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে পণ্যের বিনিময় অনুপাতও বদলেছে। ১৯৯০’র দশকে চীনকে প্রচুর পণ্য রফতানি করতে হতো প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির জন্য। এখন সে অনুপাত অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। চীনের বাণিজ্যিক শর্ত এখন তার পক্ষে।
এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা আবার সস্তা শ্রমের খোঁজে অন্য দেশ যেমন ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত বা ইন্দোনেশিয়ার দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু এতে উৎপাদন, কর্মী পুনর্বিন্যাস, চেইন পুনর্গঠনসহ বহু সমস্যা দেখা দেয়। দ্বিতীয় পথটি আরও বিপজ্জনক – চীনা অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করা এবং মজুরি কমানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যেই মার্কিন সরকার চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছে।
মজার বিষয় হলো, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আগে অভিযোগ করত চীনের পণ্য খুব সস্তা, কারণ দেশটি নাকি কৃত্রিমভাবে মুদ্রার বিনিময় হার কম রাখে। কিন্তু ২০১০ সালের পর চীন সেই নীতিকে পরিত্যাগ করে। আইএমএফ-এর অর্থনীতিবিদ হোসে অ্যান্টোনিও অকাম্পো ২০১৭ সালে বলেন, চীন মুদ্রার অবমূল্যায়ন নয় বরং মূল্য ধরে রাখতে রিজার্ভ খরচ করছে। ট্রাম্প আমলের শুল্কের চাপে ২০১৯ সালে চীন স্বাভাবিক নিয়মেই মুদ্রার মান কিছুটা কমিয়েছে, কিন্তু তা কৃত্রিম নয়।
চীন যখন মুদ্রা সস্তা রাখত, তখনও পশ্চিমা শক্তিগুলো আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে তাদের সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু ২০১০’র দশকের মাঝামাঝি চীন যখন উন্নয়নশীল যোগানদাতা নয়, বরং শক্তিশালী প্রযুক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে শুরু করে, তখন থেকেই পশ্চিমা মনোভাব বদলে যায়।
চীনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হলো মার্কিন শত্রুতা বৃদ্ধির আরেকটি বড় কারণ। গত দশকে চীন স্ট্র্যাটেজিক খাতে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। দ্রুতগতির রেল, নিজস্ব বিমান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ইলেকট্রিক গাড়ি, চিকিৎসা প্রযুক্তি, স্মার্টফোন, চিপ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে দেশটি বিশ্বসেরা। অথচ মাথাপিছু জিডিপি এখনও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ৮০ শতাংশ কম।
কেন্দ্রীয় দেশগুলোর জন্য এটি বিপদের কারণ। তাদের অর্থনৈতিক দাপট টিকে আছে প্রযুক্তিগত একচেটিয়াতা বজায় রাখার মাধ্যমে। ওষুধ, যন্ত্রপাতি, বিমান, কম্পিউটার—এসব পণ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকলে দক্ষিণের দেশগুলো বাধ্য হয় সস্তা জিনিস রফতানি করে এসব কিনতে। চীন সেই একচেটিয়াতা ভেঙে দিচ্ছে।
তাই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্তি থামাতে কাজ করছে না। বরং চীন এখন আরও বেশি করে স্বনির্ভর প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। শেষ অস্ত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র চাইছে যুদ্ধ বাধাতে। তাদের লক্ষ্য চীনের উৎপাদন ও বিনিয়োগ খাতে আঘাত হানা, যাতে সেই শক্তি যুদ্ধের পেছনে ব্যয় হয়। এই যুদ্ধ চীন কোনো সামরিক হুমকি তৈরি করছে বলে নয়, বরং তারা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করছে বলেই যুক্তরাষ্ট্র ক্ষিপ্ত।
চীনকে ঘিরে যে সামরিক হুমকির গল্প শোনানো হয়, তা পুরোটাই কল্পিত। চীনের মাথাপিছু সামরিক ব্যয় বিশ্ব গড়ের নিচে, আর যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ। চীনের পারমাণবিক অস্ত্র আটটি হলে যুক্তরাষ্ট্রের জোটের হাতে আছে অন্তত ষাটটির মতো। বিশ্বে মার্কিন ঘাঁটি শত শত, চীনের আছে মাত্র একটি—জিবুতি তে। চীন গত ৪০ বছরে কোনো যুদ্ধ শুরু করেনি, বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র এই সময়ে ডজনখানেক দক্ষিণের দেশে হামলা চালিয়েছে বা সরকার ফেলে দিয়েছে।
তাই আসল হুমকি আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই। কারণ, চীন স্বশাসিত উন্নয়নের পথে হাঁটছে। এটাই সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর জন্য ভয়ংকর। পশ্চিমা শক্তি তাদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব এত সহজে হারাতে দেবে না।
ডিলান সালিভান: সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ম্যাককোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডজাঙ্ক্ট ফেলো।