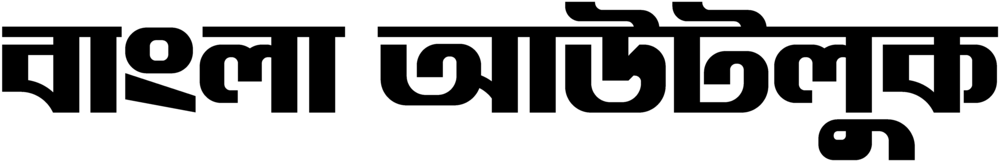বিপ্লব যাঁরা শুধু বইয়ে পড়েছেন, বিপ্লব শুরু হলে তাঁরা তাকে চিনতে পারেন না। পূর্বনির্ধারিত কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচির জামা গায়ে আসে না বিপ্লব। মুখস্থ মতবাদের বইপড়া প্রশিক্ষিত মাথা অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক কাল্ট, মাচো মস্তিষ্ক অথবা ব্যক্তিগত স্টেকহোল্ডার্স, কিম্বা ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব অথবা দল-গোষ্ঠী-পার্টিগত সংকীর্ণ পজিশন দিয়ে ঠিকঠাক চেনা যায় না তাকে। যখন সত্যি সত্যি দৃশ্যমান হতে শুরু করে গণবিপ্লব-প্রবাহ, এমনকি তখনও রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্রের বাইরেকার সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দলের মহাসচিবের মনে হতে থাকে, “এ ধরনের আন্দোলনকে তৈরি করা হচ্ছে” আসলে “দেশের মূল সমস্যা”কে “ডাইভার্ট করার জন্য”।
আরো বড়ো পরিসরে যখন জাগতে লাগে সুস্পষ্ট গণঅভু্যত্থান, সবচাইতে অগ্রসর তরুণ-যুবারা যেদিন মধ্যরাতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাগত বৈপ্লবিক বাঁকটা নেন সর্বাত্মক একনায়কের বহুকালের বিশেষ্য-বিশেষণ, ন্যারেটিভ ও বাগধারাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে, সেসবকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসার মধ্য দিয়ে, সেই দিন সকালেও বছরের পর বছর ধরে আন্তরিক একাগ্রতার সাথে গণঅভু্যত্থান নিয়ে বইপত্র লিখতে থাকা প্রবীণ বিপ্লবী দার্শনিকের মনে হতে থাকে, “তরুণরা বিদ্যমান দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তার ফ্যাসিস্ট শক্তি ও কাঠামো ... টিকিয়ে রাখতে চায়। বিদ্যমান ব্যবস্থাটা বজায় রেখে [তারা] নিজেরা দুর্নীতিবাজ আমলা, পুলিশ ইত্যাদি হতে চায়, রাষ্ট্রের চাকরি চায়।” এই বলে সতর্ক করতে থাকেন তিনি: “নৈতিকতার দিক থেকে ভাবুন, তরুণরা দুর্নীতিবাজ হতে চায়— এটাই তাদের বাসনা।”
আরেকটু পরই ১৫ বছরের একনায়কতন্ত্রকে একটানে গোড়া উপড়ে ফেলে দেবেন যাঁরা, সেই তরুণ শিক্ষার্থীদের মুক্তিপিপাসু লড়াই সম্পর্কে মহা-আত্মবিশ্বাসের সাথে এই কটাক্ষ করতে তাঁর বাধে না যে: “আমরা কতো বড় গর্তে পড়ে গিয়েছি একটু ভাবেন। এটাই তো সরকারি আমলা হয়ে দুর্নীতি করা ও সহজে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার খায়েশ ও জীবন পণ আকাঙ্ক্ষা? এটা দেখে যারপর নাই মোহিত না হয়ে উপায় নাই।” এই বলে আফসোসের সীমা থাকবে না তাঁর যে: “পৃথিবীর কোত্থাও অন্য কোন ইতিহাসে তারুণ্যের বিপুল অপচয়ের এই বিশাল নজির আপনি পাবেন না।”
কোরান শরিফের আয়াতের তীব্র সুন্দর কাব্যিক-দার্শনিক আত্মীকরণ ঘটিয়ে যে-তরুণ বিপ্লবীরা লিখেছিলেন “প্রতিটি শ্বাস একটি বিপ্লবের স্বাদ গ্রহণ করবে”, স্বপ্ন দেখেছিলেন কোনো একদিন তাঁরাও পার্লামেন্ট-ভবনে বা গণভবনে শ্রীলঙ্কার তরুণদের মতো গাইবেন “বেলা চাও” গান — সেই তরুণরাই ফ্যাসিস্ট হাসিনার হাঙ্গরের হাঁ-করা দাঁতের ফাঁকে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিবেন “বাংলা ব্লকেড” কর্মসূচির, যখন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যুক্ত হতে শুরু করবেন ঢাকা শহরের সাধারণ শ্রমজীবী-চাকুরিজীবী মানুষ, এমনকি তখনও হাসিনাশাহীর অত্যাচারে দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া আগাগোড়া লড়াকু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অনলাইন-অ্যাক্টিভিস্টের মনে হতে থাকবে, ‘ব্লকেড’ শব্দটা যেহেতু কোলকাতার, এবং “‘বাংলা ব্লকেড’ ... কথাটা” যেহেতু “একজন বাংলাদেশীর মাথা থিকা বাইর হবে না”, সুতরাং এই আন্দোলন হয়তো তৈরি করা হয়েছে ভারতের স্বার্থে হাসিনার ওপর এই মর্মে চাপ সৃষ্টির জন্য যেন সে চীনের দিকে ঝুঁকে না যায়।
অতঃপর ছাত্র-জনতার ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদের এক দফার ঘোষণায় বঙ্গভবনের দিকে ধাবমান লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল দেখে ৪০ মিনিটের নোটিশে খুনি হাসিনা যেদিন পালিয়ে যাবে ভারতে — ৩৬শে জুলাই — ঠিক তার আগের দিনও অতীব সম্মানিত একজন অধ্যাপক-সম্পাদকের মনে হতে থাকবে, “দু’পক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ার কারণেই এ ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এটা দুঃখজনক ও হতাশাজনক। ... দেশ ও জাতির জন্য এহেন হতাহতের ঘটনা অত্যন্ত ক্ষতিকর। উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা জরুরি।”
অথচ ততক্ষণে স্বয়ং হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশে তার বিভিন্ন বাহিনী মেরে ফেলেছে একজন-দুইজন নয়, হাজার-বারোশো মানুষকে। তাদের নির্বিচার গুলিতে অন্ধ হয়ে গেছেন, পঙ্গু হয়ে গেছেন, আরো হাজার হাজার লোক। ভরা-শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে অলিতে-গলিতে-রাস্তায়-মহল্লায়। এরকম একটা মুহূর্তেও নব্বই ছুঁই-ছুঁই বয়েসের প্রাজ্ঞ, আজীবন-বামপন্থী, ঐ বুদ্ধিজীবীর শান্ত-নিরাপদ মস্তিষ্ক বলতে থাকবে, “শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিতে সরকারের পদত্যাগের বিষয়টি প্রধান করে এনেছে। ... পদত্যাগ হচ্ছে একপ্রকার শাস্তি বা বিচার, সেটা দিয়ে মূল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।” এবং এখানেই থামবেন না তিনি। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের অসারতা তুলে ধরে বলতে থাকবেন সমঝোতার কথা: “এ অবস্থায় আন্দোলন দীর্ঘ সময় চালানোর চেষ্টা হলেও, মানুষ রোজ রোজ রাস্তায় নামবে না, অন্যদিকে সরকার রাষ্ট্রশক্তির চূড়ান্ত ব্যবহার করে তা থামানোর চেষ্টা করবে; মাঝখান থেকে একের পর এক নিরীহ প্রাণ ঝরতে থাকবে, সম্পদ ধ্বংস হবে। এটা কারও জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। তাই দু’পক্ষকে একটা সমঝোতায় আসতে হবে।”
ততক্ষণে হাসিনাও বলছে সমঝোতার কথা। বলছে “শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসতে চাই, তাদের কথা শুনতে চাই”। এমনকি যখন সে তার রাজকীয় তাচ্ছিল্যের অনুগ্রহ প্রকাশের ভঙ্গিতে বলছে আলোচনার জন্য “গণভবনের দুয়ার খোলা”, এবং সে খবর যখন পরের দিন ৩৫শে জুলাই সরকার-সমর্থক পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে “সমঝোতা চায় সরকার” শিরোনামে, এবং ছাত্রনেতারা রীতিমতো “ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থানে” অংশগ্রহণের আহবান জানাচ্ছেন “বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের” কাছে, তখনও এই সর্বাত্মক স্বৈরতন্ত্রী একনায়কের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় আসে না যে, এর পরের দিনই তাকে তার গণভবন ফেলে রেখে জান হাতে নিয়ে পালাতে হবে প্রতিবেশী প্রভু-পরাশক্তির কোলে। আর পলায়নপর হেলিকপ্টার উড্ডয়নের দুই ঘণ্টা আগেও তার ভারতমাতার ‘র’ ইন্টেলিজেন্স বাহিনী টেরটাও পাবে না, এতকাল তাদেরই মদদে টিকে থাকা “ঠাকুরমা ঝুলি”র রাক্ষসী রাণীর মতো মানুষখেকো এই মহিলার দৈনিক ব্যক্তিগত ভরণপোষণের দায়দায়িত্বও এবার তাদেরকেই নিতে হবে। ভবিষ্যতে শুধু এই সান্ত্বনাটুকু তারা পেতে পারবে যে, তাদের চীন-মার্কিন গোয়েন্দা-প্রতিদ্বন্দ্বীরাও একই রকম অন্ধকারে ছিল।
॥ দুই ॥
এই হলো বিপ্লব। অথরিটারিয়ান ইন্টেলিজেন্স কখনোই আন্দাজ পায় না গণবিদ্রোহের, গণবিপ্লবের। কেননা স্বতঃস্ফূর্ত গণবিপ্লব গলায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে হাঁটে না। বিপ্লবের প্রধান একটা শনাক্তকরণ চিহ্নই হচ্ছে, ঘটমান বর্তমানে চেনা যায় না তাকে। বৈপ্লবিক প্রশ্ন ওঠে: ইহা কি বিপ্লব বটে? পলিটিক্যালি কারেক্ট উত্তর আসে: “আমি বলছি না, এটা একটা বিপ্লবী আন্দোলন”। বিপ্লবের সংজ্ঞায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে, এরকম তো লেখা নাই, বাছা! মার্কস-লেনিন-খোমেনী তো এরকম বলে নি কখনো! বামবিপ্লবী হুজুরেরা বরং বারবার বলেছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী পার্টি হয় না; বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব হয় না। এটা যদি বিপ্লবই হয় তবে বিপ্লবের লেনিনটা কে, শুনি? কেইবা এই বিপ্লবের খোমেনি?
চিরমুখস্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লব এটা না। এটা কিউবার ফিদেল ক্যাস্ত্রো, চে গুয়েভারার সামরিক বাহিনীগত বিপ্লব না। এটা ইরানের ‘ইসলামী’ বিপ্লবও না। এটা উনবিংশ শতাব্দীর অ্যানালগ-আমলাতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। পরিণামে পুরাতনী ফেউ একে চিনতে পারছে না। উনিশ শতকের জ্ঞান-বুদ্ধি-তত্ত্ব দিয়ে আপনি এই চলমান গণবিপ্লব-প্রবাহের প্রকৃত পরিচয়ের কুল পাবেন না। চিরদিন চিন্তাপ্যারেড করা, বস্তাপচা ও বাতিল বুদ্ধি-সেপাইরা তাই আহাজারি করেই চলেছেন। চলছে অন্ধদের অন্তহীন হস্তিদর্শন।
অথেনটিক বৈপ্লবিক বার্থ সার্টিফিকেট নাই বলে চোখের সামনে জলজ্যান্ত বিপ্লবকে শনাক্ত করতে পারছেন না আঁতেলেকচুয়াল। বড়োজোর ‘গণঅভু্যত্থান’! এই বলে বড়ো একটা দম ফেলে হাঁসফাঁস করতে থাকেন বুকিশের দল। ঘাড়ের উপর মাথার বদলে কিছু বই নিয়ে ঘোরেন এই পণ্ডিতের পাল। জলজ্যান্ত বিপ্লবের জন্মসনদ নিয়ে গোলমাল লাগে ইনাদের। বই ছাড়া, থিয়োরি ছাড়া, দার্শনিক-হুজুরের নাম ছাড়া, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের পবিত্র গ্রন্থগত সংজ্ঞা ছাড়া নিছক নিজের চোখে, সাদা চোখে, দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে, জেনে-বুঝে-উপলব্ধি করে পাঁচটা কথা বলতে পারে না এই মুখস্থ মতাদর্শের সর্বদলীয় বিদ্বৎসমাজ। অথচ ঘটনা হলো, যাহা গণঅভ্যুত্থান তাহাই বিপ্লব।
গণঅভ্যুত্থানের তুলনায় বিপ্লবের দুইখানা অতিরিক্ত শৃঙ্গ থাকে না। সরল শব্দার্থকোষের সরল বিবরণীও জানে, সমাজের “যে সুস্থিত সত্তা উপরিস্থ থাকিয়া অভিভাবকের ন্যায় সক্রিয় হয়”, তাকে বলে “অভি”। অভির উত্থানকেই “অভু্যত্থান” বলে। যখন খোদ জনগণ রাষ্ট্রীয় ময়মুরুব্বিদেরও উপরে স্থাপন করে বসেন নিজেদের সামাজিক সত্তাকে, যখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, তাকে বলে “গণঅভু্যত্থান”। এই সেই সময় যখন মরা গাঙে বান ডাকে। ভেসে যায় পুরাতন। ভাঙনের জয়গান শুরু হয়ে যায়। প্লাবন আসে দেশজুড়ে, স্থানজুড়ে, রাষ্ট্রজুড়ে। মহাপ্লাবন। জনপ্লাবন। কারো পক্ষে নিজেকে আর ছোটো করে দেখার উপায় থাকে না। কারো পক্ষে নিজেকে আর বড়ো করে দেখার উপায় থাকে না। প্লাবন ছাড়া পলি পড়ে না। নতুন জমি জাগে না। নতুন নির্মাণ শুরু করা যায় না। নতুন সমাজের পত্তন ঘটানো যায় না। বান ডাকলে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায়— গণেশ উল্টে গেছে, বিপ্লব ঘটেছে। বিপ্লবে ‘প্লব’ থাকে। প্লবই প্লাবন। প্লাবনে সকলে ভাসে। প্লাবনে সকলই ভাসে। ভেসে যায় মসনদ, পুরাতন যাবতীয় আইকন-চিহ্ন-প্রতিমা। বৈপ্লবিক বানে ভাসে এমনকি বিপ্লবের মুখস্থ, পুরাতন, বস্তাপচা লাল বই, নীল নকশা, সবুজ বিধান।
বিপ্লব ছক কষে ঘটে না কখনো। স্বতঃস্ফুর্ত বিপ্লবের কেন্দ্রীয় সচিবালয় থাকে না। স্মলনি ইন্সটিটিউটের মতো বলশেভিক সদর দপ্তর থাকে না। বিপ্লব বুরোক্র্যাসি নয়। স্বতঃস্ফুর্ত গণঅভু্যত্থান তাই আমলাতান্ত্রিক কোনো কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং দিয়ে হয় না। মজলিশে শুরা কিম্বা পলিটবুরোর ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত কর্মসূচি ফলো করে বিপ্লব হয় না। স্ট্র্যাটেজি ও পূর্বপরিকল্পনা থাকে গুটিকয়ের অভু্যত্থানে। রাজনৈতিক দলের বা সামরিক সংস্থার বন্দুকীয় অভু্যত্থানে। এরকম অভু্যত্থানে লাগে আগে থেকে নির্ধারিত সিলেবাসভিত্তিক ‘বিপ্লবী’ তত্ত্বের বই, সহি ও মুখস্থ মতাদর্শ, আর পঞ্চবাৎসরিক রণকৌশল। বিপ্লব বুরোক্র্যাটিক নয়। বুরোক্র্যাসি দিয়ে বিপ্লব হয় না। প্রতিবিপ্লব হয়, সামরিক অভ্যুত্থান হয়। রাষ্ট্রের, আদালতের, সেনাবাহিনীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের, পরিবর্তনকামী পত্রিকার, এমনকি পেশাদার বিপ্লবীদের রাজনৈতিক পার্টিগুলোরও আনুষ্ঠানিক আমলাতান্ত্রিক হায়ারার্কি থাকে। স্বতঃস্ফুর্ত গণবিপ্লবে বৈচিত্র্য থাকে, হায়ারার্কির উচ্চনিচ-কাঠামো থাকে না। রাজনৈতিকতাময় সামাজিক বন্ধুত্বের অর্গানিক নেটওয়ার্ক থাকে। এ জিনিস গড়ে ওঠে ব্যথিতদের বেদনার আনুভূমিক গঠনকাঠামো দিয়ে। বিপ্লব চিরকালই স্বতঃস্ফূর্ত আর গণ। বিপ্লব মানেই স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব। বিপ্লব মানেই গণবিপ্লব। আকাশ থেকে বিনামেঘে বাজ পড়ার মতো নেমে আসে বিপ্লব । আড়ালে তিলে তিলে সিঞ্চিত শ্রাবণের মেঘে জমা বৈদ্যুতিক শর্তাবলী চট করে গোচরে আসে না। সব তত্ত্ব চমকে যায় বৈদ্যুতিক বজ্রপাতে। শেখানো বিপ্লববুদ্ধি রাতারাতি লোপ পায়। থ মারে থতমত বিদ্বৎসমাজ।
রাজতন্ত্র এবং জমিদারির হাজার হাজার বছরে আমাদের কোষে কোষে জমে আছে কর্তার ইচ্ছায় কর্মের চিন্তাদাসত্ব। কর্তাপ্রথার বীজ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সাম্রাজ্যের, রাষ্ট্রের ও সমাজের কর্তৃত্বপরায়ণতা হয়তোবা সহজেই শনাক্ত করা যায় কিন্তু যেটা উনবিংশ শতকে বসবাসকারী িবপ্লবীরা সহজে দেখতে পান না তা হলো, “বিবাহে — পরিবারেও — মতাদর্শ রয়েছে দেদার” । প্রচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন যত মতাদর্শ— মাতব্বরির। বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষাময় ব্যক্তিরও আত্মা আর ঘরের ভেতরে থাকে পিতৃত্বের-কর্তৃত্বের ভূত। চিন্তাদাসত্বের গড্ডলিকা-প্রণালীর ভেতরে লুকিয়ে থাকে কর্তাপ্রথার ক্রমিকতা। পিতৃতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ চিন্তাপ্রণালীর লোকেরা তাই বৈধ বৈবাহিক পিতা খোঁজেন বিপ্লবের, অথবা অনুমোদিত নেতা। পৈতা খোঁজেন তাঁরা বিশুদ্ধ বিপ্লবী ব্রাহ্মণের। আগে থেকে নির্ধারিত, বিশুদ্ধ, বৈপ্লবিক তত্ত্বাবলী খোঁজেন। মুখে তাঁরা বলেন ঠিকই “জনতার বিপ্লব, জনতার দ্বারা বিপ্লব, জনতার জন্য বিপ্লব” কিন্তু খোদ জনতার হাতে বিপ্লবকে ছেড়ে দেওয়ার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন না। জনতার পক্ষ থেকে জনতারই অভিভাবক হয়ে উঠতে চান তাঁরা। তাঁরা ভাবেন জনতার জ্ঞান নাই, বৈপ্লবিক বিজ্ঞান নাই। জনতার কাজ শুধু জিন্দাবাদ বলা। আর নেতার পেছনে হাঁটা। কামলা খাটা— গায়ে ও গতরে। বিপ্লব, তাঁরা ভাবেন, বিপ্লবী আমলাদের কাজ। অথচ চিরটা কাল ইতিহাস দেখিয়েছে, আড়ালে বন্দুক নিয়ে, পেছনে লোক জুটিয়ে, মহামতি ধুরন্ধর কৌশলী নেতা আর পলিটিক্যাল পার্টি মিলে ক্ষমতা দখলের ‘অভ্যুত্থান’ এক জিনিস, বিপ্লব অন্য জিনিস। এক কিম্বা একাধিক আমলাতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে, স্বঘোষিত বিপ্লবী নেতার নেতৃত্বে যত বিপ্লবের গল্প শোনা যায়, সেগুলো ‘অভু্যত্থান’ মাত্র। ছলে-বলে-কৌশলে সামরিক অভু্যত্থান। প্রায়শই প্রকৃত গণক্ষমতার বিপরীতে সামরিক প্রতিবিপ্লব মাত্র। কখনো কখনো লোকে তাতে খুশি হতে পারে বটে, আন্তরিক অংশগ্রহণ থাকে না তাদের। এরকম অভু্যত্থানে কয়েক শত কিম্বা কয়েক হাজার সমর্থকের সোচ্চার উল্লাসের আলোকচিত্রকে গণঅভু্যত্থান বলে চালানোটা ইতিহাস-গ্রন্থে চলে, বিপ্লবে চলে না। “ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই হলো বিপ্লবের সবচাইতে সন্দেহাতীত বৈশিষ্ট্য। ... বিপ্লবের ইতিহাসের প্রথম কথাটাই হলো ... শাসকতার জগতে জনসাধারণের প্রবল প্রবেশ।”
তিন শ বছর ধরে রাশিয়া শাসন করা জারতন্ত্রের যেদিন পতন ঘটে, মুখস্থ মতাদর্শে প্রশিক্ষিত পেশাদার বিপ্লবীরা টাশকি খেয়ে যায়। সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবে সবচেয়ে সামনের সারিতে থাকেন তরুণ ছাত্র আর সাধারণ মেহনতি মানুষ। আগামাথা না বুঝে নেতারা দৌড়ান পিছে পিছে। তাঁদের পেছনে থাকে পুরাতনী রাজনৈতিক দল। আর সবার পেছনে থাকে কনফিউশনে ভুগতে থাকা বুদ্ধিজীবীর পাল। উদ্ভ্রান্তের মতো বিড়বিড়িয়ে তাঁরা বলতে থাকেন, “কাজটা কি ঠিক হচ্ছে”, “কাজটা কি ঠিক হচ্ছে”। তাঁদের কথায় কান না দিয়ে সমস্ত কিছুকে পর্যালোচনার অধীনে আনে বিপ্লব।
॥ তিন ॥
রাজশক্তিকে ফেলে দিয়ে বিপ্লব মাথা তুলে দাঁড়াতেই না দাঁড়াতেই এসে পড়ে প্রতিবিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াশীল, গুপ্ত, পঞ্চমবাহিনীর সোচ্চার ও সক্রিয় উপস্থিতির চিহ্ন। তাঁরা শুধু দোষ ধরেন— “ঐ যে মূর্তি ভাঙলো”! তাঁরা শুধু খুঁত বের করেন। ঐ দ্যাখো, বিপ্লবপ্রবাহে যাঁরা শত শত হত্যায় সায় দিয়েছিল উচ্চকণ্ঠ কথা দিয়ে, নিঃশব্দ নীরবতা দিয়ে, সেই চিরবেঈমান, চিরদুঃখিতরা আজ বাধা পাচ্ছে পুরাকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রপিতার তরে মায়াক্রন্দনে। ফেসবুকে তারা খুব হেঁয়ালি রচনা করে বলতে থাকে, “এ কেমন বিপ্লব! আমাদের অধিকার নাই! পিতৃশোক-প্রকাশের স্বাধীনতা নাই!” তারা বলে, “দুষ্কৃতিরা তলে তলে চেক করছে আমাদের টাইমলাইন! একনায়কের প্রতি আমাদের পক্ষপাত গোপন থাকছে নাকো, হায়! আমাদের প্রাইভেসি নাই হয়ে গেছে! এর নাম বিপ্লব! এই জন্যই কি আমরা বিপ্লব করেছিলাম? এরই জন্য কি এত এত শহীদের আত্মদান?” আহ! পঞ্চমবাহিনী দেখে মনে হয়, বিপ্লবকে আটকানো যায় নি যেহেতু, বিভ্রান্তি ছড়ানোর অধিকারই বিপ্লব।
বিপ্লবে এই এক বড়ো চিহ্ন বটে— মানুষের মুখে মুখে, ফেসবুকে, বাক্যের অবাধ প্রকাশ। হাসিনাৎসির রাজত্বকালে এতকাল কথা বলতে হতো ভান-ভনিতায়, ঠারেঠুরে, অভিনয় করে, আর সাংকেতিক সান্ধ্যভাষায়। রাজনৈতিকভাবে মূক ও বধির হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ সমাজ। সর্বশেষ মেষ ছিল সর্বাত্মক সরকারি ইন্টারনেট শাটডাউন। বিপ্লব রাতারাতি জাদু দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে গোটা জরামরা সমাজের আপামর মানুষকে। কথা বলছেন তাঁরা ফ্যাসিবাদ বিলোপের পথ নিয়ে, অধিকার-স্বাধীনতা নিয়ে। এমনকি দু-দিন আগের শাসকের ছদ্মবেশী সমর্থক ছুপালীগও করে যাচ্ছে কত কত কলকল। তিনাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আতঙ্ক অস্থিরতা পৌঁছাচ্ছে আকাশ অবধি। প্রশ্ন তুলছে তারা নিজেদের বাক- আর শোক-স্বাধীনতার। তাতেই প্রমাণ মিলছে, প্রকৃতই বিপ্লব ঘটেছে। সত্যি সত্যি শতফুল ফুটছে এবার। বিকশিত হচ্ছে শত মত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই বিপ্লব পর্যাপ্ত গণতান্ত্রিক বটে। বহুস্বর, বহুমত, বহুকেন্দ্র এই গণবিপ্লবের গড়নেই আছে।
ছিমছাম হয় না বিপ্লব। ক্যাওস, বিশৃঙ্খলা, হাজার রকমের কথা, আর অজস্র মতামত বিপ্লবের সাধারণ লক্ষণ। যে কখনো কথা বলে নি, সেও আজ কথা বলছে। যে কখনো রাষ্ট্রের পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে কোনো মত দেয় নি, সেও বলছে কী করা উচিত, আর কী করা ঠিক না। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস, আর কুজ্ঝটিকা-কুহেলিকা বিপ্লবের চিরন্তন হাওয়া। পুরাতন সমস্ত শাসনচিহ্নের প্রতি আউলাঝাউলা গণক্রোধ বিপ্লবের প্রাথমিক ঝাপট। অরাজকতা— সে তো বিপ্লবের অংশ চিরকাল। ফরাসি বিপ্লবেও ছিল। রাজতন্ত্রের বিপরীতে গণবিপ্লবের অরাজতন্ত্র চির-অর্গানিক।
এরই মধ্যেও থানা ফেলে, বন্দুক-ইউনিফর্ম ফেলে, প্রায় পুরো পুলিশবাহিনীর আত্মগোপন এবং তিন-তিনটা দিবস-রজনী জুড়ে পরিপূর্ণ সরকারহীনতা এই জায়মান বিপ্লবপ্রবাহের সামাজিক স্বরাজের অসামান্য উজ্জ্বল স্বাক্ষর। আত্মপরিচালনার সামাজিক সক্ষমতা জেগে উঠছে পূর্ণাঙ্গ উৎসাহে। নেটজুড়ে, পাড়ায় পাড়ায়, আর মোড়ে মোড়ে আপামর মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সামাজিক মেলামেশার সংগঠন জেগে উঠছে প্রবল আগ্রহে। প্রত্যেকেই ভাবছে আজ এদেশ আমারও। দেশ নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে, আইন ও সংবিধান নিয়ে আমিও লিখতে পারি, বলতে পারি, পাঠচক্র করতে পারি। কর্তব্য আমারও। উপরন্তু প্রবল ফ্যাসিস্ট শত অত্যাচার সত্ত্বেও আগাগোড়া নারীদের প্রবল উপস্থিতি বিপ্লবের বিশেষ দৃশ্যরূপ। সবাই সবার সাথে মিলেমিশে ভিজতে থাকে বর্ষাবিপ্লবে। বৃষ্টির সাথে মেশে শহিদের উজ্জ্বল লাল রক্তধারা। শ্রাবণের প্রবল বর্ষণে মেশে আশুরার মর্সিয়া, কারবালার কান্না-হাহাকার। এত যে বৃষ্টি তবু তৃষ্ণার্ত সন্তানের জন্য পানি নিয়ে পথে নামে মায়েরা-বাবারা। দিগন্ত-প্রসারিত আবু সাঈদের হাতে মিশে যায় লক্ষ লক্ষ হাত। ব্যক্তিতে-সমষ্টিতে জেগে ওঠে আন্দোলনের আধ্যাত্মিকতা , সম্মিলিত রুহানিয়াত। আগুন, গুলি আর মৃত্যু-অধ্যুষিত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নানাবিধ ফেতনা-ফ্যাসাদ আর বিভেদ-বিভক্তিগুলো পার হয়ে আসতে থাকে নানাবিধ দল-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়। জুলাই-শ্রাবণময় ধারাপাতে ভিজতে থাকে মিছিলে মিছিলে যত হিজাব ও বোরখার পাশাপাশি টিশার্ট ও জিনস। স্কুল-কলেজের আর মাদ্রাসার-ভার্সিটির প্রোগ্রামে-কর্মসূচিতে, স্লোগানে-গ্রাফিতিতে, মুখস্থ মতাদর্শের এতকালের অনতিক্রম্য বিভাজনগুলো সব পড়ে থাকে নতুন বৃষ্টিতে ধোয়া জুলাইয়ে জেগে ওঠা এজমালি ভাষার পিছনে। সর্ববিধ ক্যাওস ও গণ্ডগোল পার হয়ে এগোয় বিপ্লব। পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে প্রতিদিন নিন্দুকের মনে দুঃখ দিয়ে।
॥ চার ॥
মুক্তি সবাই চান কিন্তু মুক্তি এসে হাজির হলে ভয় পান অনেকে। কেননা মুক্তির সব দায়দায়িত্ব নিতে হয় মুক্ত মানুষকে নিজেকেই। বাকিরা দোষারোপ করেন। বোঝাতে চান তাঁরা, শৃঙ্খলেই মঙ্গল। যেন সর্বাত্মক স্বৈরতন্ত্রের শৃংখলই ভালো ছিল— আমরা মুক্তির উপযুক্ত নই। এইসব দোষারোপকারী দালালদের যুক্তির শেষ নাই, বিদ্যাবুদ্ধির অন্ত নাই।
চলমান গণবিপ্লব-প্রবাহের সামনে সবার প্রথমে এলো মন্দিরে-বাড়িঘরে হামলা। পেছনের পেছনে এলো কত যে নালিশ। এলো গুজব। এলো উদ্বেগ। এলো আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, হাহাকার, আহাজারি। যত দোষ বিপ্লব ঘোষ। গণঅভ্যুত্থান করাটাই অপরাধ হয়ে গেছে যেন। আরো এলো হাসিনার ঘাপটি মারা দালাল যত সব। হিন্দুদের জন্য তাদের মায়াকান্নার শেষ নাই। অথচ এই গত পূজার সময়ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা রানা দাশ গুপ্ত আঙুল তুলেছিলেন হাসিনা সরকারের দিকেই। কে না জানে, গত ১৬ বছর হিন্দুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার রাজনীতি করেছে আওয়ামী লীগই। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সময়পর্বে “অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন" প্রণয়ন করেছিল তারাই। সেই আইনের ছত্রছায়ায় কেড়ে নিয়েছিল হাজার হাজার হিন্দুর জমি। হাসিনা পালানোর পরে পাহারায় বসলো লোকে মন্দিরে-বাড়িঘরে হামলা ঠেকাতে। মাদ্রাসার ছাত্ররা যোগ দিল রাত-পাহারায়।
তারপর এলো ডাকাতি। ডাকাতির অজস্র গুজব। ডাকাত-লীগে যেন ভরে গেল দেশ। আবারও পাহারা বসল গণমানুষের। ডাকাতির বিরুদ্ধে পাহারা। গুজবের বিরুদ্ধে, ভয়ের বিরুদ্ধে, আতঙ্কের বিরুদ্ধে পাহারা। রাত জাগল সারা বাংলাদেশ।
এক মাস না যেতেই নেমে এলো বিকট বন্যা। সীমান্ত ডিঙিয়ে এলো। ত্রিপুরার ডম্বুরের রিজার্ভয়ার উপচে পড়া ঢল এলো। ভেসে গেলো কুমিল্লা। ভেসে গেলো ফেনী। ছাত্রদের আহবানে জুলাইয়ে জেগে ওঠা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের তরফে রাতারাতি গড়ে উঠলো কোটি কোটি টাকার গণতহবিল। খাদ্য-ওষুধ গেল, অন্য ত্রাণসামগ্রী গেল, ট্রাকে চেপে নৌকা গেল, মানুষের পাশে গিয়ে মানুষ দাঁড়াল, শিল্পীর পোস্টারে এলো নতুন স্লোগান “যত বিপদ তত ঐক্য”। বিপদ আসছে, ভয় আসছে, কোটি টাকা প্রজেক্টের প্রোপাগান্ডা আসছে। উদ্দেশ্য মানুষকে ভয় দেখানো। কিন্তু মানুষ ভয় পাচ্ছে না। মানুষ সংগঠিত হচ্ছে। বিপ্লব তৈরি করে নিচ্ছে সবাইকে।
॥ পাঁচ ॥
ছাত্রতরুণেরা নেতৃত্ব দিয়েছেন বিপ্লবের। এই বিপ্লব বাংলাদেশের ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থান। এই বিপ্লব বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার বিপ্লব। গঠনবিন্যাস এর ইন্টারনেটের মতো। নেটওয়ার্কগুলো এর স্বাধীন, উন্মুক্ত, বিকেন্দ্রীভূত, গণতান্ত্রিক, বহু কণ্ঠের এবং সহযোগিতামূলক। আবার, ইন্টারনেটই কিন্তু এই গণবিপ্লবের অন্যতম হৃৎপিণ্ড, রক্তচলাচলতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র। এই বিপ্লব একক কেন্দ্রহীন। পুরোপুরি কেন্দ্রহীন নয়। পূর্বনির্ধারিত অনড় আকারের বাইরে এর আছে শিথিল, অ্যামোর্ফাস, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক-সামাজিক নিউক্লিয়াস। সমাজ নিজেই যেহেতু প্রাকৃত সত্তা, ‘সামাজিক’ অর্থ তাই প্রাকৃতিক, ন্যাচারাল, স্বাভাবিক। একক কেন্দ্রহীন, একক ও আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বহীন হলেও এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছে, ক্রমশ বেড়ে উঠেছে, আনুভূমিক একটা নেটওয়ার্ক-নিউক্লিয়াসের নেতৃত্বে।
আনুভূমিক নেটওয়ার্কেরও কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস থাকে বৈকি। নিউক্লিয়াস মানেই তো কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস। আনুভূমিক নেটওয়ার্কেরই বরং নিউক্লিয়াস জিনিসটা থাকে। টপ-ডাউন বুরোক্র্যাটিক নেটওয়ার্কের থাকে পিরামিডের চূড়াসম, উচ্চতম, কর্তৃত্ব-কমিটি। গণমানুষের রক্ত-মাংস-দেহ দিয়ে গড়া একটা পাদদেশের ঘাড়ে সেটা চেপে বসে থাকে। ‘কেন্দ্রীয়’ কমিটি বলা চলেই না তাকে। ‘কেন্দ্রীয়’ তো ‘কেন্দ্র’ থেকে। কেন্দ্র মানে বৃত্তের কেন্দ্র। আর সমাজের বৃত্ত মানে অনেক বৃত্ত। তার কেন্দ্রও অনেক। স্বতঃস্ফুর্ত সামাজিক মহা-গণআন্দোলনের স্বভাব মহাসাগরের মতো, বায়ুমণ্ডলের মতো, ঝড়ের চোখের মতো। তাতে করে অনেক স্রোতের, অনেক পরিধির, অনেক বৃত্তের এবং অনেক কেন্দ্রের পারস্পরিক, ওভারল্যাপিং, ক্রস-কানেকশনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে আপাত-অদৃশ্য এক শিথিল নিউক্লিয়াস। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না তাকে, অথচ সে থাকে।
নেটওয়ার্ক হচ্ছে ইন্টারনেটের সংগঠন। নেটওয়ার্ক হচ্ছে সমাজের আদিতম ইনবিল্ট প্রতিষ্ঠান। ডিফল্ট, প্রাকৃতিক সংগঠন। নেটওয়ার্ক হচ্ছে দেহ-কোষ-শরীরের সহজাত সংগঠনপ্রণালী। নেটওয়ার্ক মানে কানেকশন। মানবীয় যুক্ততা। প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎপ্রবাহ। নেটওয়ার্ক বলতে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের মুক্ত-স্বাধীন যোগাযোগ-বিন্যাস। প্রতিটা নেটওয়ার্কের প্রতিটা নোড মুক্ত, স্বাধীন, স্বপরিচালিত। সমাজ বলতে পেশাকেন্দ্রিক, পাড়ামহল্লাকেন্দ্রিক, আগ্রহকেন্দ্রিক, কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক, বয়সকেন্দ্রিক, জেন্ডারকেন্দ্রিক, বিভিন্ন সৃজনশীল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতাকেন্দ্রিক কোটি কোটি নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক। ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান-প্রবাহও তাই মুক্ত-যুক্ত অজস্র নেটওয়ার্ক দিয়ে গড়া একটা রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক। এ হলো স্বতঃস্ফূর্ত, স্ব-পরিচালিত, বহু স্বরের, বহু রঙের, বিকেন্দ্রীভূত, আনুভূমিক, ছাত্র-গণআন্দোলনের ধারাবাহিক যোগাযোগ-প্রবাহ। গঠিতব্য নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর প্রাথমিক বিন্যাসও তাই রচিত হোক আন্দোলন-অভ্যুত্থান-ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কসমূহের প্রাকৃত বিন্যাসে। মূলগতভাবে এর আমলাতান্ত্রিক হওয়া চলবে না। উঁচুনিচু কর্তৃত্বতন্ত্র মার্কা জিনিস হলে চলবে না। নতুন ধারার নতুন নতুন রাজনৈতিক দলও হোক জুলাইবিপ্লবের মতো নেটওয়ার্ক-সংগঠন।
॥ ছয় ॥
এই বিপ্লব মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলা শত শত তাজা মানুষের জীবনের মূল্যে কেনা, হাজার হাজার মানুষের অন্ধ্বত্বের-পঙ্গুত্বের দামে কেনা সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত গণবিপ্লব। এ জিনিস সস্তা না। এ জিনিস প্রতিদিন আসে না। এ যখন আসে, সব কিছুকে ঠেলে নিয়ে যায়। সব কিছু দৌড়ায় সামনের দিকে। মুক্তির দিকে।
অসম্ভব দ্রুতগামী এক ঝড়ের গতিতে পূর্ণতর বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। আক্ষরিক অর্থেই অজস্র মানুষের বিপ্লব। প্রত্যক্ষভাবে যারা এই বিপ্লবের কাজে নেমে পড়েছেন তারা নিজেরাও কতটা খেয়াল করছেন তা আমি জানি না কিন্তু বাংলাদেশ একটা দীর্ঘস্থায়ী গণঅভ্যুত্থান-প্রবাহের ভেতর দিয়ে তুমুল বেগে অগ্রসর হচ্ছে মহাবিপ্লবের দিকে। এই বিপ্লব-প্রবাহ কোথায় গিয়ে থামবে কেউ বলতে পারে না। বলা যায় না, গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে বদলে দেবে বাংলাদেশের জুলাই-বিপ্লবপ্রবাহ। এর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ইজ্জত, ইনসাফ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আকুতি।
অকল্পনীয় দ্রুততর লয়ে সময়, সমাজ এবং মানুষকে তৈরি করে নিতে নিতে এগিয়ে চলেছে এই গণবিপ্লব। আপনা-আপনি তৈরি হচ্ছে সব। জেগে উঠছে গোটা সমাজ— একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাপটে যেটা ডুবে যেতে বসেছিল দু-দিন আগেই। যে-দুই তরুণ রাগ করে কথা বলতেন না অনেক দিন, তাঁরা এখন হাতে হাত রেখে রাস্তা সামলাচ্ছেন সারাদিন। বিপ্লব মানে বন্ধুত্ব। ছোটো ছোটো বিভেদ ও অভিমান ম্লান করে দিচ্ছে বিপ্লব। ব্যক্তিগত দুঃখ কিম্বা অপার হতাশা আর টিকতে পারছে না। সক্রিয় হয়ে উঠছেন প্রত্যেকেই। এসবের পাশাপাশি ভেঙে পড়ছে চিন্তা-বন্ধুত্ব-সংগঠনের পুর্বতন বিন্যাস। অথচ একা হয়ে যাচ্ছেন না কেউ। বিপ্লব সব কিছু নাড়িয়ে দিয়েছে। কাউকে নির্লিপ্ত আর থাকতে দিচ্ছে না বিপ্লব। নতুন করে তৈরি করে তুলছে প্রত্যেককে। চিন্তায়, কথায়, তৎপরতায়। কাউকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেবে না সে আরো বহু দিন। আপনি টেরও পাচ্ছেন না, অথচ আপনিও তৈরি হয়ে উঠছেন আরো বড়ো বড়ো ঢেউয়ের জন্য।
মনোযোগ দিন। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নিজের নিজের মতো করে স্থানীয়ভাবে, পাড়ায়-মহল্লায়-কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। গড়ে তুলুন নিজের নিজের এবং নিজেদের নেটওয়ার্ক সংগঠন— যত ছোটোই হোক তা। এই বিপ্লব আপনারও। এটা আসলে বহু বহু ছোটো ছোটো বিপ্লব ও অভ্যুত্থানের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, চলবে। ধাপে ধাপে সে নিজেকে মেলে ধরছে ক্রমশ। নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে ক্রমাগত। আগের ধাপেও কেউ জানে না পরের ধাপে কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ। প্রতি মুহূর্তে চলমান, পরিবর্তমান পরিস্থিতিসমূহের পরবর্তী গতিপ্রবাহ সত্যি সত্যি কোন কোন বাঁক ঘুরে কোন দিকে অগ্রসর হবে সেটা ঠিকঠাক মতো অনুমান করতে পারাটা আজ মোটেই সহজ কাজ নয়। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান গণঅভ্যুত্থান-প্রবাহ সম্ভবত বাংলাদেশের সমাজ এবং রাষ্ট্রের আমূল বৈপ্লবিক সংস্কার সম্পন্ন করতে চলেছে বড়োজোর দশক খানেকের মধ্যেই। এখনই প্রশ্ন তুলুন: স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কোন পথে হবে। কোন পথে যাবেন আপনি।
সমস্ত রাজনৈতিক দলকে চোখে চোখে রাখুন। একটা দলও তার নিজের গঠনতন্ত্র মোতাবেক গণতান্ত্রিক দল নয়। সব দলই দলের ভিতরে ভিতরে কাঠামোগতভাবে আমলাতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক। তাদের নেতা সব আজীবন নেতা। শেখ হাসিনার একনায়কতন্ত্র একদিনে তৈরি হয় নি। আকাশ থেকে পড়ে নি। ১৯৭২ সাল থেকে গত ৫০ বছর ধরে সবগুলো রাজনৈতিক দল দেশের রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের হাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেওয়ার ধান্দা করেছে। যে যেভাবে পারে। ছলে বলে কৌশলে। এটা একটা সর্বদলীয় শয়তানির টুর্নামেন্ট ছিল। শেখ হাসিনা তাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। কিন্তু টুর্নামেন্টের সব রাজনৈতিক দল মিলেই কিন্তু টুর্নামেন্টটা সম্পন্ন করেছিলেন। অন্য কেউও চ্যাম্পিয়ন হতে পারতেন কিন্তু। ফলাফল একই হতো। এই প্রথমবারের মতো ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানে ঘটেছে গণশক্তির উদ্বোধন। নতুন একটা ‘বাংলাদেশ-বন্দোবস্ত' তৈরি করার দিকেই তারা এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ৫০ বছরের শয়তানির টুর্নামেন্টের ইতি ঘটতে চলেছে এবার।
এনালাইটিক্যাল কম্পাস হিসেবে কাজ করতে পারাটা আমাদের জন্য জরুরি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আন্দোলন-প্রবাহের গতিপ্রকৃতি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করা, অনুমান করা, বিশ্লেষণ করা, প্রকাশ করা, লেখা, সবার সামনে বিভিন্ন বিকল্প তুলে ধরা, পরমতসহিষ্ণু এবং বহুমতনির্ভর সমাজের কথা তুলে ধরা— এগুলো এখনকার জরুরি কর্তব্য।
বিপ্লব চলমান। জুলাই চলছে। তৈরি হোন দীর্ঘমেয়াদী এই বিপ্লব-প্রবাহের জন্য। দেশ যেমন কারুর বাপের না, স্বতঃস্ফূর্ত এই গণবিপ্লবও কারো বাপের না। এই বিপ্লব আপনার। আপনি এতে অংশগ্রহণ করুন। তাহলে পেছনে আর ফিরবে না বাংলাদেশ। এই বিপ্লব দূরগামী, দীর্ঘমেয়াদী। আমাদেরকে ভবিষ্যৎ দেখতে পারতে হবে এবং মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে আসন্ন ইতিহাসের নির্মীয়মান ছবি, কেননা বিপ্লব শুধু রক্ত দিয়ে হয় না। চিন্তা দিয়ে হয়। চিন্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চর্চার মধ্য দিয়ে হয়। জুলাইবিপ্লবের শহীদেরা, আহত যোদ্ধারা, আমাদের নয়নমণি। কিন্তু বিপ্লব নিছক কোনো শহিদি প্রকল্প নয়। বিপ্লব নিজেই এক মুক্তভাবে বাঁচার ইশতেহার।
* * *
প্রাসঙ্গিক তথ্য : গত ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মিলে খুব তাড়াহুড়া করে এই “ইশতেহারের খসড়া”র প্রথম পাঠটা লিখেছিলাম। বন্ধু মনজুরুল আজিম পলাশের উদ্যোগে ১৭ই আগস্ট ২০২৪ সেটা পড়া হয়েছিল কুমিল্লায় তাঁদের “যৌথ খামার”-এর অনুষ্ঠানে। আমার যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারি নি। পলাশ নিজেই এটা পড়েছিলেন। সেটা তখন তাঁদের পক্ষ থেকে ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানেই বিতরণ করা হয়েছিল ও রচনার কাগজে মুদ্রিত কিছু কপি। অনুষ্ঠানটা হয়ে যাওয়ার পরে ঐ রাতেই ১০টার দিকে পোস্ট করা পলাশের আহবানে যারা সাড়া দিয়েছিলেন, তাদের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন এর পিডিএফ-কপি। বর্তমান রচনা ইন্টারনেট আর্কাইভে আপলোড করে রাখা সেই আদি পিডিএফ-কপিরই পরিমার্জিত ও ঈষৎ-বর্ধিত পাঠ। ডেডলাইনের বিড়ম্বনায় এবং আমার এলোমেলোমির পরিণামে আদি এবং বর্তমান খসড়ার মধ্যবর্তী কালপর্বে দুটো ‘আধামার্জিত’ পাঠ চলে গেছে ঢাকার বাংলা একাডেমির একটা বইয়ে এবং কলকাতার “জনসাহিত্য” পত্রিকায়। ফেরানোর উপায় ছিল না। আশা করি, “জুলাইবিপ্লব: ইশতেহার ও অনুষঙ্গ” নামে প্রকাশিতব্য আমার বইয়ে প্রকাশিত হবে এই “চলমান ইশতেহারের খসড়া”র চূড়ান্ত পাঠ, আরো কিছু সম্ভাব্য সংশোধন ও পরিমার্জনার পর। সরন, রাবি: ৩রা আগস্ট ২০২৫।