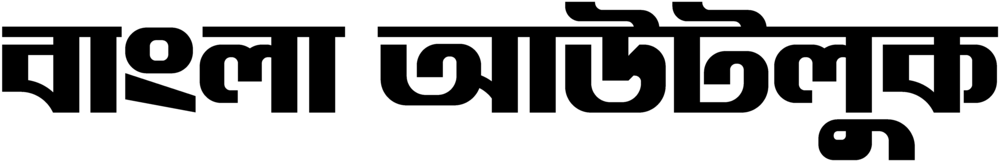জুলাইয়ের গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক জাগরণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা
সালাহউদ্দিন আহমেদ রায়হান
প্রকাশ: ০১ আগস্ট ২০২৫, ০২:১৬ পিএম

২০২৪ সালের জুলাই এক অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের সাক্ষী হয়ে ওঠে, যার কেন্দ্রে ছিলেন দেশের বিভিন্ন পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, শিল্পী, কার্টুনিস্ট ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। এই জাগরণ ছিল শুধু রাজপথে প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং মানুষের মনোজগতের গভীরে দোলা দেওয়া এক সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান, যা প্রতিরোধের ভাষা, সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ এবং গণআন্দোলনের অবয়বে ধরা দেয়। জুলাই আন্দোলন যেমন এক মাসব্যাপী ওঠানামার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তেমনি প্রতিটি পর্বে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সক্রিয়তা ও প্রতিরোধ আন্দোলনের গতি নির্ধারণ করেছে।
১৪ জুলাই শেখ হাসিনার বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য ছাত্রসমাজকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। এই অবজ্ঞাসূচক বক্তব্যের জবাবে তারা প্রতিবাদকে রূপান্তর করে এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ভাষায়। “তুমি কে, আমি কে? রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার!”— এই স্লোগান শুধুই শব্দ নয়, এটি হয়ে ওঠে ছাত্রদের হাতে তীব্র প্রতিরোধের সাংস্কৃতিক অস্ত্র। সেই মুহূর্তেই একটি নতুন জাগরণের উন্মেষ ঘটে।
১৬ জুলাই আবু সাঈদের মৃত্যুর পরে স্লোগানের গর্জন হয়ে ওঠে আরও তীব্র, “লাশের ভিতর জীবন দে, নইলে গদি ছেড়ে দে”— এই ভাষার মধ্যে নিহিত ছিল এক দিকে শোক, অন্য দিকে অপরিহার্য বিপ্লবের দাবির ঘোষণা। ১৯ জুলাই ইমার্জেন্সি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছে যায়। শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়, হতাহত বৃদ্ধির আশঙ্কাজনক ট্রেন্ড। এই দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন শিক্ষক, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীসহ নানা পেশার মানুষ। তারা নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে, আন্দোলনের ভিত মজবুত করেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সায়মা ফেরদৌস ও সামিনা লুৎফার নেতৃত্বে গঠিত হয় “বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক”, যেখানে শিক্ষকরা এক ছাতার নিচে সমবেত হন প্রতিবাদে। “সন্তানের পাশে অভিভাবক” নামে সংগঠন গড়ে তোলেন রাখাল রাহা, কবি মাহবুব মোর্শেদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আসফিয়া আজিম। “দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ” নামে চলচ্চিত্রকার আকরাম খান, অমিতাভ রেজা চৌধুরী ও মামুনুর রশীদের উদ্যোগে সংগঠিত হন প্রভাবশালী শিল্পীরা। এই সব সংগঠন নিজেরাই গড়ে ওঠে, সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিছক দায়িত্ববোধ ও মানবিকতা থেকে। তাদের সক্রিয়তা এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতার মধ্যে আশার আলো হয়ে উঠেছিল। যদিও প্ল্যাটফর্ম আলাদা, উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন— শেখ হাসিনার পদত্যাগ।
কার্টুনিস্টদের অবদান ছিল বৈপ্লবিক। মেহেদী হক, আসিফুর রহমান, রায়িদ হোসেনসহ অসংখ্য কার্টুনিস্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কার্টুনকে পরিণত করেন প্রতিবাদের আগ্নেয়াস্ত্রে। প্রায় ৫৫০টি কার্টুন আঁকা হয়, যার মধ্যে আহসান হাবীবের “কাউন্টডাউন”, আসিফের “নাটক কম কর পিও” বিশেষভাবে জনমনে সাড়া ফেলে। দেবাশীষ চক্রবর্তীর পোস্টারও ছিল আন্দোলনশীল মানুষের চেতনা জাগ্রত করার অন্যতম উপায়। শুধু ঢাকাতেই প্রায় হাজারের অধিক দেয়ালে প্রতিবাদী গ্রাফিতি আঁকা হয়, যেন রাজধানীর ইট-পাথরের প্রতিটি দেয়াল হয়ে ওঠে কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর।
সেজানের “কথা ক” এবং হান্নানের “আউয়াজ উডা” গান ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমজীবী মানুষ ও বুদ্ধিজীবিদের এক কাতারে এনে দাঁড় করায়। এই সময় “শূন্য” ব্যান্ডের পুরনো গান “শোন মহাজন” নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে আন্দোলনের ভাষ্য হিসেবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায় ৪০টি নতুন গান আপলোড হয় আন্দোলন-সংশ্লিষ্টভাবে, যার মধ্যে ৩১টি ছিল RAP গান— সরাসরি দ্রোহ ও প্রতিবাদের আবেগে ভরপুর, তরুণদের মুখে মুখে ফিরে বেড়ানো এক সাংস্কৃতিক স্লোগান।
২৯ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী আবৃত্তি করেন নবারুণ ভট্টাচার্যের সেই প্রতিকূল বাস্তবতার কবিতা— “এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না! এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না”— যা ক্ষণিকেই ভাইরাল হয়ে পড়ে এবং মানুষের চিন্তাকে নতুন করে নাড়া দেয়। ৩২ জুলাই, বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শামীমা সুলতানা তাঁর ব্যক্তিগত অফিস থেকে শেখ হাসিনার ছবি নামিয়ে প্রতিবাদ জানান, যা সাহসিকতার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে ওঠে।
জাতীয় পত্রিকায় নাম গোপন করে “একজন ডাক্তারের দিনলিপি” নামে লিখেন এক ইন্টার্নী ডাক্তার শামীমা আক্তার, যেখানে তিনি তুলে ধরেন শত শত গুলিবিদ্ধ, রক্তাক্ত দেহের চিকিৎসা দিতে গিয়ে কিভাবে তাদের দিন-রাত একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাটি কেবল চিকিৎসকের আত্মকথন নয়, এটি আন্দোলনের ভেতরকার যন্ত্রণা ও মানবিকতার দলিল হয়ে ওঠে।
আসিফ নজরুল, রেজওয়ানা চৌধুরী ও দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য নেতৃত্ব দেন “বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজে”-র ব্যানারে গঠিত মানববন্ধনে, যেখানে ডিবি অফিসের সামনে ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবিতে অবস্থান নেওয়া হয়। আইনজীবী মনজুর আল মতিন ও সারা হোসেন হাইকোর্টে রিট করেন, কারাবন্দী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে।
বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক বদরুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষক ও প্রকৌশলীরা ২ এবং ৩ জুলাই ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করেন, যেটি পূর্ববর্তী আন্দোলনেরই একটি সাংগঠনিক সম্প্রসারণ। এই সময়েই আয়োজিত হয় সবচেয়ে বৃহৎ পেশাজীবি ও বুদ্ধিজীবি সমাবেশ, “দ্রোহ যাত্রা”, যেখানে শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ নানা শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্ব ঘটে। সব সংগঠন একত্রিত হয়ে এই সমাবেশকে পরিণত করে বৃহত্তর জাগরণের অনিবার্য সমাপ্তি বিন্দুতে, যার নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।
জুলাই আন্দোলন এগিয়েছে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। ১৪ ও ১৬ তারিখের তাৎক্ষণিক শক্ত উত্তরণ এবং ১৯ তারিখের কারফিউ, ডিবি'র দপ্তর থেকে সরকারপ্রণীত বিবৃতি, একদিকে আন্দোলনকে কিছুটা শ্লথ করলেও বাইরে থাকা সমন্বয়কদের ঐকান্তিক প্রতিজ্ঞা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আন্দোলনকে আবার জ্বালিয়ে তোলে। তখন দেশের রাজপথে, অলিগলিতে, ভার্চুয়াল জগতে— সবখানে উচ্চারিত হতে থাকে একটিই অদম্য দাবি— শেখ হাসিনা ও আওয়ামিলীগ সরকারের পতন।
সরকারি গেজেট অনুযায়ী জুলাই আন্দোলনে নিহত হন ৮৪৪ জন। জাতিসংঘের প্রাথমিক পরিসংখ্যান জানায়, নিহতের সংখ্যা ছিল ১৪০০-র বেশি, আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৩ হাজার। শহীদদের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন ২৮৮ জন— যাদের অধিকাংশই ছিলেন রিকশাচালক, অটোচালক, নির্মাণ শ্রমিক। শিক্ষার্থী শহীদ হন ২৬৯ জন, ১৮ বছরের নিচে শিশু শহীদ হয়েছেন ১৮১ জন। এদের মধ্যেই ছিলেন ৬ বছর বয়সী রিয়া গোপ ও ৪ বছরের আহাদ— যারা হয়ে ওঠে এক নিষ্পাপ আন্দোলনের নিষ্ঠুরতম প্রতিচ্ছবি। গোটা দেশ যেন তখন এক মৃত্যুপৃথিবীতে রূপ নেয়— যেখানে ফ্যাসিস্ট হাসিনা, আমি আর ডামি নাটকীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে, রক্ত ও ধ্বংসের রাজনীতি চাপিয়ে দেন।
তবু, এই নিপীড়নের মধ্যেই জন্ম নেয় এক গভীর সাংস্কৃতিক জাগরণ। মানুষের মনোজগতে রচিত হয় এক নতুন চেতনার ভিত্তি। বহু বছর পরে দেখা যায়, দেয়ালের লেখা ও গ্রাফিতি ফিরে এসেছে ঢাকাসহ সারা দেশে— মানুষ যেন ইট-পাথরের শহরকে নিজের প্রতিবাদের ক্যানভাসে রূপ দেয়। একসময়ের বিলুপ্তপ্রায় স্যাটায়ার কার্টুন নতুন জীবনের রূপ পায়। ছাপা গণমাধ্যমে প্রায় নির্বাসিত এই রূপ হঠাৎ করেই জনতার অনুপ্রেরণায়, ফেসবুক-টুইটার-ইনস্টাগ্রামে পুনর্জন্ম নেয়। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে রূপান্তরিত প্রতিবাদের ভাষা— স্লোগান।
“কোটা না মেধা? মেধা, মেধা!” দিয়ে শুরু হলেও আন্দোলনের প্রগাঢ়তা বাড়তেই আওয়ামিলীগ প্রশ্ন তোলে— বিকল্প কে? তখনই সাধারণ মানুষ ব্যঙ্গের সুরে, প্রতিজ্ঞার সাহসে নতুন স্লোগান তৈরি করে— “তুমি কে, আমি কে? বিকল্প, বিকল্প!”। এরপর যেন এক বহমান ঢেউয়ের মতোই রাজপথে ও অনলাইনে উচ্চারিত হয়, “আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম, সংগ্রাম!”, “দালালি না রাজপথ? রাজপথ, রাজপথ!”, “আসছে ফাল্গুনে, আমরা দ্বিগুণ হব!”— এই স্লোগানগুলো শুধু বাক্য নয়, ছিল একেকটি মানসিক ঐক্যের পতাকা।
এই সময় পেশাজীবিরা ছিলেন অস্বাভাবিকভাবে সক্রিয়— চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, আইনজীবি, শিক্ষক সবাই নানা ঝুঁকি নিয়েও জনতার পাশে এসে দাঁড়ান। যারা দীর্ঘদিন আওয়ামিলীগের ছত্রছায়ায় থেকে আত্মবিক্রয়ের গ্লানিময় পথ বেছে নিয়েছিলেন, তারা নির্লজ্জ নীরবতায় কিংবা ক্ষমতাকেন্দ্রিক যুক্তির পক্ষে মুখ খুলেছিলেন। তাদের বিপরীতে দাঁড়ানো বিবেকবান পেশাজীবিরা সাহস ও আন্তরিকতায় জনতার পাশে ছিলেন, দিকনির্দেশনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, আন্দোলনকে সৃষ্টিশীলতা ও মেধার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলেছেন।
এই সম্মিলিত প্রয়াসের ফলাফল বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। স্বাধীনতার ৫৪ বছরে এই প্রথম একটি সরকার প্রধান— প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা— তাঁর পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, মন্ত্রিসভার সদস্য ও সংসদের প্রতিনিধিদের নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পর্যায়ের কর্মীদের ফেলে রেখে পালিয়ে যান। তখনই মানুষের মুখে মুখে উঠে আসে সেই সর্বশেষ আরাধ্য স্লোগান— “পালাইছে রে পালাইছে— শেখ হাসিনা পালাইছে!”