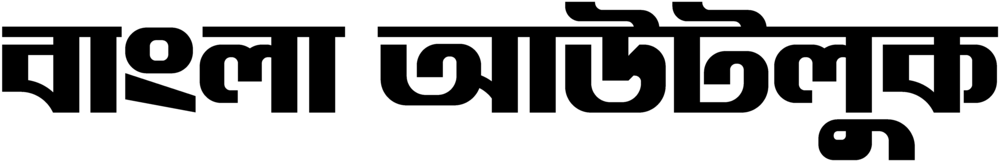অস্থিতিশীলতা, অবিশ্বাস আর নাভিশ্বাস যেখানে মিলেমিশে একাকার হয় অভিন্ন মোহনায়, সেটার একটা সাধারণ নামও দেওয়া যেতে পারে, ‘বাংলাদেশের রাজনীতি’। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে এখানকার রাজনীতি পরিণত হয়েছে এক অদ্ভুত এবং চলমান কাব্যে। এই কবিতার বইতে প্রতিটি পাতায় লেখা হচ্ছে মানুষের নিত্য নতুন আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম, জিজ্ঞাসা ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের রক্তমাখা শব্দ, বর্ণ ও অক্ষর। সেই কাব্যে নতুন অধ্যায়ের প্রতীক্ষা চিরকালীন। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে আমরা যেন সেই কাব্যের একই পৃষ্ঠা বারবার পড়ছি—কোনো নতুন পঙ্ক্তি নেই, নতুন সুর নেই, নেই কোনো অভ্যন্তরীণ বিবর্তনের আভাস।
সম্প্রতি একটি আলোচনাতে এই বাস্তবতার নির্যাস উঠে এসেছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌসের একটি বক্তব্যে। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি দৈনিকের আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় তিনি বললেন, ‘আমাদের রাজনৈতিক নেতারা নতুন কোনো পথে হাঁটছেন না। তারা যেন ক্ষমতার পুরোনো গলিপথেই অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছেন—যেখানে মতবিনিময়ের চেয়ে হিসাব, আদর্শের চেয়ে সমঝোতা, এবং জনগণের চেয়ে পৃষ্ঠপোষকের খাতিরটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।
অধ্যাপক ফেরদৌস স্পষ্ট করে তুললেন, বিএনপি কিংবা জামায়াতে ইসলামীর মতো দলগুলোর মধ্যেও কোনো মৌলিক রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস বা নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে না। তারা ‘জনপ্রতিনিধিত্বশীল’ হলেও আদতে আগের মতোই কাঠামোবদ্ধ চিন্তাধারায় আবদ্ধ। মাঠের রাজনীতি, নির্বাচনী বোঝাপড়া, কথিত ‘জাতীয় ঐকমত্য’ কমিশনের কৌশলী উপস্থিতি—এসবই যেন পুরোনো ঘোড়ার নতুন সাজ। আর নতুন দলে, যেমন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)—সেখানেও প্রত্যাশিত পথচ্যুতি না দেখে হতাশ হয়েছেন অনেকে।
তবে এই রুদ্ধচক্রের মাঝেও আশার ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়েছিল ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে। সাধারণ মানুষ দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে রাজপথে নেমেছিল—তা নিছক উত্তেজনায় নয়, বরং গভীর রাজনৈতিক বোধ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়। অধ্যাপক ফেরদৌস আরও বললেন, এমনকি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অনেক অনুসারীও তখন রাস্তায় নেমেছিলেন। এটি ছিল এক সত্যিকার অর্থে বিস্তৃত সামাজিক আন্দোলন—যা কোনো দলের দয়ায় আসেনি, এসেছিল জনগণের নিজস্ব আর্তি থেকে।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই গণপ্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক ফসল খুব দ্রুতই বিকৃত হয়েছে। সরকার গঠনের প্রক্রিয়াটি হয়ে উঠেছে রহস্যময়। উপদেষ্টারা কীভাবে মনোনীত হলেন? সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল ঠিক কী? জনগণের সেই ঐক্য ও ত্যাগ কোথায় প্রতিফলিত হলো রাষ্ট্রযন্ত্রে? এসব প্রশ্ন শুধু অমীমাংসিতই নয়, বরং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েও গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।
অধ্যাপক ফেরদৌস আরও বললেন, তরুণ নেতৃত্ব—যারা তখন বিকল্প কণ্ঠ হিসেবে সামনে এসেছিল—তাদের অনেককে 'দুর্নীতিগ্রস্ত’ বলেই চিহ্নিত করা হলো। এই কলঙ্ক আরোপের প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত সুনিপুণ। কোটি টাকার ফান্ড, নানা ব্যবসায়িক প্রলোভন, নৈতিক দুর্বলতার গল্প ছড়িয়ে দিয়ে যে রাজনৈতিক তরঙ্গ জন্ম নিতে পারত—তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। তরুণদের চরিত্রহনন আজ আমাদের জাতীয় অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। অথচ এদের অনেকেই ছিল আদর্শিক, সংগ্রামী এবং রাজনৈতিকভাবে জেনুইন।
অধ্যাপক সাঈদের বক্তব্য একপাশে রাখলে পুরো দৃশ্যপট এখানেই শেষ নয়। বর্তমান সরকার, যা মূলত একটি সিভিল সোসাইটি-নির্ভর শাসনব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তারা আসলে কী চায়? আদতে তারা তো ঠিক গোড়াতেই একটি গভীর সমস্যায় জর্জরিত। তাদের আত্মঘাতী কিছু সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরকে অবিশ্বাস জাগাতে করেছে। রাজনীতিবিদ, আমলা, সরকারি কর্মচারী—সবার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একরকম অবজ্ঞাসূচক ও সন্দেহপ্রবণ। অথচ প্রশাসনের ভেতরেও বহু নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা থাকতে পারেন। তারা তো বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করে যাচ্ছেন। এই ধরনের নির্বিচার অবিশ্বাস তাদের জন্য শুধু রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাই তৈরি করেনি। বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দৃম্যমান অনেক দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে।
অনেকের কাছে এখন একই প্রশ্ন —এই অবরুদ্ধ অবস্থার পরিবর্তন কোথা থেকে আসবে? সেটা কেবল নতুন দল দিয়ে নয়, বরং নতুন মত, পথ ও ভাষা দিয়েই সম্ভব। একটি রাজনৈতিক ভাষা, যা মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। একটি পথ, যা ইতিহাসের কাঁধে চড়ে নয়, বরং সময়ের প্রয়োজনকে ধারণ করে তৈরি হবে। একটি মত, যা দলীয় সীমারেখা নয়, মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে।তবে এই মূল্যবোধ জনগণের জাগ্রত করবে কে? আর কোন বিশেষ উদ্যোগ এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে।
সহজ হিসেবে দুর্বল কিছু রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী চাইছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে চুইংগামের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে টেনে দীর্ঘ করতে। ওদিকে বাংলাদেশের সবথেকে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বি এনপি চাইছে নির্বাচন। তাদের এই দাবি নতুন কিছু নয়। বিগত আঠারো বছর ধরে তাদের সংগ্রাম এই নির্বাচনকে ঘিরেই। তারা শুরু থেকেই একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দাবি করে আসছে। বর্তমানে তাদের রাজনীতির মূল বক্তব্যে কোনো সংযোজন বিয়োজন ছাড়াই সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। জামায়াত ইসলামীর বক্তব্য অভিন্ন নয়। তারা কখনও যেমন দ্রুত নির্বাচন চাইছে। আবার আন্দোলনের বাস্তবতায় দরকষাকষিতে মেতে তারাও চাইছে নির্বাচন না হোক।
ওদিকে যারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছেন তাদের মধ্যে অনতম নেতা হিসেবে পরিচিতি ফরহাদ মজহার অভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে বলেছেন, ‘অবশ্যই গণ–অভ্যুত্থান পথ, নির্বাচন না। নির্বাচন করার মানে হচ্ছে ওই পুরোনো লুটেরা মাফিয়া শ্রেণিকে আবারও আনবেন। ঠিক এনসিপিও সেটাই শিখছে। হ্যাঁ, নির্বাচনই করতে হবে। ওরাও ঠিকই চাঁদা চাইতেছে, বড় বড় হাউসের কাছে যাচ্ছে। দুই কোটি টাকা, পাঁচ কোটি টাকা।’ তার বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে তিনি চাইছেন যেভাবে যাই হোক নির্বাচন না হলেই চলে। তার এই দাবির মূল কারণ নিজ স্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে টিকে থাকা নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সেটা বোঝা কঠিন। তবে এটুকু বোঝা যায় তিনি কোনোভাবেই নির্বাচন হতে দিতে চাচ্ছেন না। এবং এইজন্য তিনি ন্যারেটিভের বাজারে নিত্যনতুন পন্য এনেই চলেছেন।
সুক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বাংলাদেশের চলমান সংকটে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে জনগণের প্রত্যাশা খুব বেশি কিছু নয়। তারা শুধু আস্থার পরিবেশ, ন্যায্যতার পথ এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার একটা উপযুক্ত কাঠামোর বাইরে তেমন কিছু হাতিঘোড়া চাইছেন না। ওদিকে নাগরিক জীবনে স্বস্তি ফেরাতে বাজার নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলার পুনর্বিন্যাস, শিক্ষানীতির সংস্কার এগুলো তো চাইবেই। তবে এসবের জন্য কেবল প্রশাসনিক দক্ষতা নয়, দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। অথচ বাস্তবতা হলো, এসব প্রশ্নে দলগুলো আজও নীরব, উদাসীন, কিংবা সংকীর্ণ স্বার্থে বিভ্রান্ত আর সেটাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারত বর্তমান অধ্যাপক ইউনুসের নেতৃত্বাধীন সরকার।
তবে বাস্তবতা পুরোপুরি উল্টো। স্বাস্থ্যখাতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন নূরজাহান বেগম। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে কোনোকিছু না বুঝে গণমাধ্যমে ব্রিফ করার বাইরে কিছুই করতে পারেন নাই সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আদিলুর রহমান শুভ্র কিংবা আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে সবার অভিযোগের অন্ত নাই। মোস্তফা সারোয়ার ফারুকির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সরাসরি ফ্যাসিবাদ তোষণের। ওদিকে ছাত্র উপদেষ্টাদের থেকে একজন পদত্যাগ করার পর যে দুইজন রয়েছেন তাদের অবস্থানও স্বস্তিদায়ক নয়।
বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে দেখলে মনে হয় উনি দীর্ঘদিনের রক্ত আমাশয়ের রোগী যার পক্ষে একটা বেসরকারি আনসার বাহিনীতে তৈরি সিক্যুরিটি এজেন্সি চালানোও সম্ভব নয়। এমনি কারণে বেশিরভাগ উপদেষ্টার নিয়োগের পর মনে হয়ে ঘোড়ার সামনে আরেকটা গাড়ি জুড়ে দেওয়া হলো।
শুরু থেকে উপদেষ্টা পরিষদের ব্যর্থতার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বর আমাদের হতাশ করেছে। আমার বিশ্বাস তাদের দেখলে মনে হয় কবি ‘কুসুম কুমারী দাশ’ তার বিখ্যাত আদর্শ ছেলের স্টাইলে লিখতেন ‘আদর্শ প্রশাসক’। আর তার লাইন হতো অনেকটা এমন–
আমাদের দেশে পাবো সেই মন্ত্রী কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
‘দেশকে কিছু দিতে হবে’ – এই যার পণ৷
অধ্যাপক ইউনুসের উপদেষ্টা পরিষদের দৃশ্যমান ব্যর্থতার বিপরীতে আমরা এক বৈপ্লবিক কালান্তরে দাঁড়িয়ে আছি। এইখানে পুরোনো কাঠামো ভেঙে নতুন চিন্তার জন্ম দিতে না পারলে, আজকের অস্থিরতা কাল হয়ে উঠবে স্থায়ী অবক্ষয়। তাই এখনই সময়—একটি নতুন রাজনৈতিক চেতনাকে রচনা করার। যেখানে রাজনীতির ভাষা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, পথ হবে সৃজনশীল এবং মত হবে নৈতিকভাবে উজ্জ্বল।
লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।