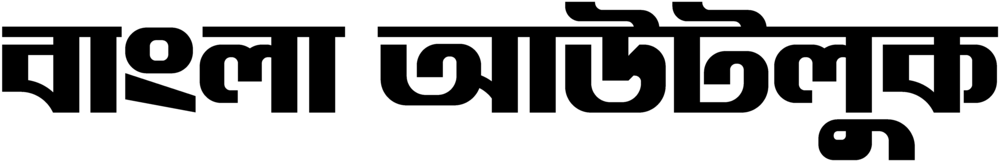সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের দাবির আড়ালে ষড়যন্ত্রের শঙ্কা

জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাওয়ার ন্যূনতম সক্ষমতা নাই এমন একটি গোষ্ঠী দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করে আসছিল। তারা যখন নানামুখী বিভ্রান্তি সৃষ্টি, মব লিঞ্চিং আর জনতুষ্টিবাদী গালগল্প সামনে রেখে প্রায় সফল হওয়ার পথে ঠিক তখনই বাধ সাধলো তারেক-ইউনুস বৈঠক। তারপর যথারীতি নির্বাচনের আনুমানিক সময়কাল নির্ধারিত হয় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। আর এতে করে দেশের সিংহভাগ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও পরাজিত গোষ্ঠী নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে শুরু করে।
দেশের প্রতিটি মানুষ জানে এই পি আর তথা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য কি পরিমাণ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে পারে। সংখ্যানুপাতিক (Proportional Representation বা PR) নির্বাচন পদ্ধতির নামে জাতীয় আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের বিপরীতে কিছু কথা শুরুতেই বলে নিতে হচ্ছে। বিশেষত, সংখ্যাপাতিক বা PR নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে যারা সওয়াল করছেন, তাদের অবস্থান কেবল রাজনৈতিকভাবে দুর্বল নয়—তা একরকম জনবিচ্ছিন্ন। তাই তারা এই প্রস্তাবনা মতো একটি আত্মঘাতী রাজনৈতিক কৌশল বেছে নিয়েছে।
অনেক দল এতে করে সুবিধা প্রাপ্তির চিন্তা করলেও তা বাস্তবে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সরাসরি হুমকির মুখে ফেলবে। বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঞ্চলে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ ভবিষ্যতে ভয়াবহ জটিলতার জন্ম দিতে পারে। বিভিন্ন বহিঃশক্তির প্রত্যক্ষ মদদে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। তারা মওকা বুঝে সংসদে প্রতিনিধিত্ব পেয়ে যাবে—এমন আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। তখন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রতিটি স্তরে তারা প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করবে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পয়েন্ট অব অর্ডারে তারা বাগড়া দিতে চেষ্টা করবে, যা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য চরম বিপজ্জনক।
বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে যখন নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তখন সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা বা PR (Proportional Representation) ব্যবস্থার প্রস্তাবনা নিয়ে যে ঢেউ উঠেছে, তা নিছকই একটি নির্বাচন পদ্ধতির সংশোধনী নয়—বরং এটি এক গভীর রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের আলামত। এই প্রস্তাব এমন এক আত্মঘাতী কৌশল, যার মধ্য দিয়ে জাতির স্বাধীনতা, ভূখণ্ডিক অখণ্ডতা ও জনগণের সার্বভৌম মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠনের অধিকার হুমকির মুখে পড়তে পারে।
প্রথমত, PR ব্যবস্থার সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো—এটি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকা রাজনীতিকদের জন্য এক ধরনের ‘ব্যাকডোর’ থেকে সংসদে ঢোকার স্পেস তৈরি করে। যারা জনসম্পৃক্ততা হারিয়েছে, জনগণের ভালোবাসা ও বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ, এবং যাদের কোনো রাজনৈতিক শিকড় নেই মাটিতে—তারাই এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদে প্রবেশ করতে চায়। এদের রাজনৈতিক শেকড় নেই, তবে লোভ আছে অগাধ ক্ষমতার। অতীতে তাদের কেউ ছিল স্বৈরাচারের দোসর , তারা সুযোগ বুঝে গিয়েছিল সামরিক ছায়ায়। তবে তারা সবসময় ক্ষমতা কেন্দ্রের কাছে মাথানত করেছে অনেকটা ধারাবাহিকভাবে।
‘সুশীল’ও ‘অভিজাত’এই মুখোশ পরে সংসদে প্রবেশের পথ যাঁরা খুঁজছে তারা এই ভুতুড়ে ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে একটি ‘রিটায়ারমেন্ট ক্লাব’ বা ‘পুনর্বাসন কেন্দ্র’ হিসেবে দেখতে চায়। এখানে কোনো দল চাইলে তাদের দলপ্রধানের স্ত্রীর দুলাভাই থেকে শুরু করে তার প্রিয় আমলা, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী এবং প্রিয়পাত্র সুশীল সমাজের সদস্যরাই ঠাঁই পাবে। জনগণের সমর্থনের বদলে তাদের সংসদে প্রবেশের একমাত্র যোগ্যতা হবে দলপ্রধানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও প্রাসাদসুলভ তোষামোদ। এরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং গোষ্ঠীর স্বার্থ ও ক্ষমতার বলয়ের রাজনীতি করবে—এবং তাতে গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা নিভে যাবে।
শঙ্কা হচ্ছে একবার যদি PR পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে ভবিষ্যতে সেই পদ্ধতি থেকে সরে আসার রাজনৈতিক সাহস বা সামর্থ্য কোনো সরকারেরই থাকবে না। একে ‘ইতিহাস’ হিসেবে হাজির করা হবে, বলা হবে জনগণের ভোটের অধিকার সংরক্ষণের প্রয়াসে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো—এই পদ্ধতির আশ্রয়ে কিছু ক্ষমতালিপ্সু গোষ্ঠী নিজেরা ব্যর্থ হয়েও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চায়।
আজ যারা PR ব্যবস্থার সবচেয়ে জোরালো সমর্থক, তাদের দিকে তাকালে এই সত্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভুঁইফোড় অনেক রাজনৈতিক দল, যাদের রাজনৈতিক ভিত্তি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন, এবং যাদের নেতা-কর্মীদের প্রায় কেউই নিজ আসনে জয়ের আশা করতে পারেন না—তাদের কাছে PR হলো একমাত্র পথ সংসদে ফেরার। এদেরকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করছে জামায়াতে ইসলামী। কারণ দেশের প্রতিটি আসনে প্রচুর ভোটার আছে তাদের কিন্তু সেটা এমপি ইলেকশন করে জেতার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু তারা যদি সংখ্যানুপাতে নির্বাচন করে সেখানে পুরো দেশের ভোট কুড়িয়ে নিয়ে বেশ ভাল সংখ্যক সিট তারা সংসদে পেতে পারে। কিন্তু তাদের ছায়া সংগঠন যেমন চরমোনাই, এনসিপি প্রভৃতিও একই নীতি অবলম্বন করছে। তাদের বাইরে আছে সিপিবির মতো জনবিচ্ছিন্ন মাইকসর্বস্ব অনেক দল। তাদের প্রায় সবাই জানে, সরাসরি ভোটে তারা জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু পুরো দেশের সব ভোট গুছিয়ে একটা সিট পেলেও পেতে পারে তারা।
যাইহোক, প্রথমত, এই পদ্ধতির ফলে “জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি” বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। বিষয়টি সহজভাবে বোঝাতে গেলে—ধরে নেওয়া যাক, ঢাকার কোনো একটি আসনে তিনজন হেভিওয়েট প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন—‘ক’, ‘খ’ এবং ‘গ’। কিন্তু PR পদ্ধতির ফলে দেখা গেল, তাদের প্রত্যেকেই এমপি মনোনীত হয়েছেন—নিজ নিজ দলের ভোট শতাংশ অনুসারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই তিনজন কি ঢাকার ঐ আসনের এমপি হবেন? উত্তর—না। তারা কেউই আসলে সেই আসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ তারা সেখানে প্রত্যক্ষ ভোটে জয়লাভ করতে পারবেন না। তাদেরকে এমপি হতে হবে একটি ছক কাটা সমীকরণের ভিত্তিতে। সেখানে সমগ্র দেশের ভোট শতাংশ অনুসারে দলে পাওয়া আসন বণ্টনের মধ্যে ভাগ বসিয়ে। এভাবে একজন এমপি হলেও, তার কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। তিনি একপ্রকার ভাসমান সাংসদ, যিনি সংসদীয় এলাকার মাটি ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন।
আবার কল্পনা করুন উপরে নির্বাচিত এই তিনজনের মধ্যে একজনকে পঞ্চগড়ের বোদা, আরেকজনকে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি এবং তৃতীয়জনকে নেকমরদের আসনে মনোনীত করা হলো। প্রশ্ন হলো—এই ব্যক্তিরা কি ওই এলাকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারবেন? তাদের কি জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে? উত্তর হলো—না। এমন একজন ব্যক্তি যিনি ওই এলাকার মানুষদের দেখেননি, জানেন না তাদের দাবি-দাওয়া, তিনি কীভাবে সেই এলাকার জনসেবা করবেন? এতে তৈরি হবে মারাত্মক গণতান্ত্রিক বিচ্যুতি। জনগণের প্রত্যাশা ও প্রতিনিধিত্বের মাঝে সৃষ্টি হবে গভীর দূরত্ব, যা একসময় সামাজিক ভয়াবহ রকম সামাজিক ক্ষোভে রূপ নেবে।
এই ব্যবস্থার আরেক ভয়ংকর পরিণতি হবে—রাষ্ট্র পরিচালনায় অস্থিরতা ও প্রশাসনিক জটিলতা। কারণ, সংসদে এমন সব লোক বসবেন, যাদের জনগণের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। তারা মাটি থেকে উঠে আসেনি, বরং রাজনৈতিক ব্যাকডোর দিয়ে প্রবেশ করেছে। এতে নাগরিকদের আস্থা যেমন হারাবে, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থিরতা, সহিংসতা, এমনকি জঙ্গিবাদী চক্রের উত্থানও ঘটতে পারে। কারণ, যেখানে জনগণ নিজ প্রতিনিধি খুঁজে পায় না, সেখানে অবিশ্বাস ও হতাশার পরিবেশ গড়ে ওঠে—এবং সেখানেই বাসা বাঁধে চরমপন্থা।
তাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে—শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার মোহে পড়ে কি আমরা এমন একটি আত্মঘাতী পথ বেছে নেবো? যাদের নিজেদের এলাকায় জনগণের ভোটে এমপি হবার মতো জনপ্রিয়তা নেই, তারাই আজ PR-এর পক্ষে সবচেয়ে বেশি সরব। অথচ তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে—তাদের ব্যর্থতার দায় কি অন্য কারো ওপর চাপানো যায়? বিশেষ এমন দলগুলো—যারা কখনোই জনগণের প্রকৃত ভালোবাসা ও সমর্থন পায়নি—তারা এখন PR ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের সংসদে ঢুকিয়ে নেওয়ার পথ খুঁজছে।
এতদিনেও তারা জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেনি। এ দায় কি বিএনপির? বিএনপি কি কখনো তাদেরকে সরাসরি ভোটের রাজনীতিতে বাধা দিয়েছে? তাতো দেইনি বরং স্বৈরাচারবিরোধী লড়াইতে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সবার ভোটাধিকার অর্জন ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে পাশে থেকেছে। আজকের এই সময়ে এসওে যদি তারা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এর দায় তো ঐসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের রাজনৈতিক দীনতা ও নীতিহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাদের জনপ্রিয়তা না থাকার স্কেপগোট হিসেবে বি এন পিকে বলী দিতে চায় কেনো তারা?
তবে কি বিএনপিকে ঠেকাতেই এই রাষ্ট্রঘাতী পদ্ধতির পক্ষে এত তৎপরতা? যদি নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আপনাদের এতো সন্দেহ থাকে, তাহলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন। চাইলে উপযুক্ত ওয়াচডগ রেখে তারপর ভোটগ্রহণ করুন। তাই বলে রাষ্ট্রের সার্বিক কাঠামো পরিবর্তন করে একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য বলা যায় না। বরং চাইলে রাজনৈতিক সমঝোতার পথও খোলা রাখতে পারেন। বিএনপির এক্ষেত্রে উচিত হবে, যারা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে, তাদের সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এটা সম্ভব না হলে পরাজিত ও পলাতক বৃহৎ শক্তির মদদে দেশ উত্তাল করা হবে। জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হওয়ার পরেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হতে হবে এটা নিশ্চিত করে আগেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।
কয়েকজন ব্যর্থ রাজনীতিকের ক্ষমতালিপ্সার ফল হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপদে পড়তে হবে এটা কাম্য নয়। আমরা সংস্কার চাই, তবে সেটা রাষ্ট্রবিনাশী নয়, রাষ্ট্রীয় বিধান সম্মত হওয়া চাই। মনে রাখতে হবে—অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত, গোটা জাতিকেই পেছনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ সাইট ও অনলাইন মাধ্যমে প্রচুর প্রচারণা চলছে এই মর্মে যে ‘বিএনপি ছাড়া প্রায় সব ছোট রাজনৈতিক দল এই ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট’।
কারণটাও সহজ, তারা জানে, সরাসরি ভোটে তারা শূন্য আসন পাবে অথবা বেশিরভাগ সিটে জামানত হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। PR ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে তারা অন্তত ১-৩টি কিংবা কেউ কেউ ১০-১৫টি আসনও পেয়ে যেতে পারে। এমন আশায় বিভোর হয়ে তারা এখন গণতন্ত্রের মূল কাঠামো তথা জনগণের সরাসরি ভোটকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বাজি রাখতে চায়।
কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—একটি রাষ্ট্র কি জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ কিছু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজের সার্বভৌম ভিত্তিকে দুর্বল করতে পারে? জনগণের প্রত্যক্ষ মতামত ও ভোটাধিকার কি রাজনীতির ছদ্মবেশী ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত? এসব প্রশ্নের উত্তর জাতিকে খুঁজে নিতে হবে এখনই, কারণ কাল হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।
আজ দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দূরদৃষ্টি। দরকার সেই সাহস, যা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের মতো রাষ্ট্রবিরোধী অন্তঃঘাতী ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। গণতন্ত্র মানে কেবল ভোট নয়—গণতন্ত্র মানে জনগণের বিশ্বাস, তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা। PR সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরায়, ছিদ্রপথে অবিশ্বাস্য ও অজনপ্রিয় শক্তিকে প্রবেশাধিকার দেয়। তাই , গণতন্ত্রের নামে যে নতুন স্বৈরতন্ত্রের বীজ বোনা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি। রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে, জনগণের হাতেই থাকতে হবে নির্বাচনের চাবিকাঠি। কোনো পেছনের দরজা নয়, গণমানুষের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার যে চিরচেনা সুসজ্জিত তোরণ, সেটাই হোক রাজনীতির একমাত্র প্রবেশপথ।