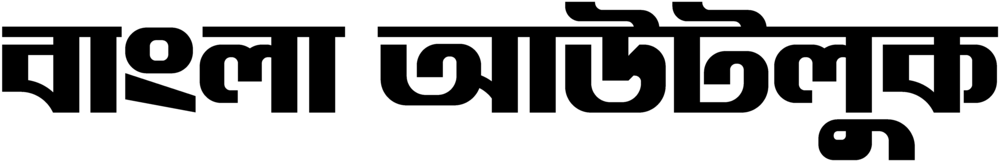আজ বাজেট ঘোষণা
মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়ানো

অর্থনীতির জটিল বাস্তবতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সোমবার বিকাল তিনটায় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এই বাজেট ঘোষণা করবেন রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে। এবারের বাজেট নিয়ে জনমানসে যে প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তা হলো—এই বাজেট কি মানুষকে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিতে পারবে? অথবা কর্মসংস্থানহীনতা, বিনিয়োগ স্থবিরতা এবং আয়ের বৈষম্যের বাস্তবতায় সরকার কি সত্যিই একটা দৃশ্যমান পরিবর্তনের বার্তা দিতে পারবে?
এই মুহূর্তে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অভাব। বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনও বলছে—কৃষি, শিল্প, সেবা—সব খাতে কর্মসংস্থান কমেছে। নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আর এই বিনিয়োগ স্থবিরতার কারণেই দেশের উৎপাদন, আয় ও রপ্তানিতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না। যে কোনো টেকসই উন্নয়নের জন্য যা দরকার, সেটি হলো স্থিতিশীলতা ও আস্থা। সেই আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বাজেটে সরকারকে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বিশেষত ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা দরকার।
অবশ্য বাজেট প্রস্তুতকারকেরা বলছেন, এটি বাস্তবভিত্তিক ও কল্যাণমুখী হবে। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে যে সংকোচন দেখা যাচ্ছে—সেটি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস নয়, বরং রাজস্ব ঘাটতির প্রতিফলন। প্রবৃদ্ধির হার ৫.২৫ শতাংশ ধরা হলেও বাস্তবতা বলছে—গত অর্থবছরের মতো এবারও তা ৪ শতাংশের নিচে নামতে পারে। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ১.৭৯ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। শিল্প খাতেও স্থবিরতা বিরাজ করছে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি তো হচ্ছেই না, বরং বেকারত্ব বাড়ছে।
এমন বাস্তবতায় বাজেটে ব্যক্তি আয়কর কাঠামো সহজকরণ, ছোট উদ্যোক্তাদের ওপর করের চাপ হ্রাস এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির প্রতিশ্রুতি ইতিবাচক। তবে এগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যদি আমলাতান্ত্রিক বাধা থেকেই যায়, তাহলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বাজেটে প্রস্তাবিত ন্যূনতম করের ধারণাটি ভালো, কিন্তু সেটির পরিধি ঠিক না হলে এটি নিম্ন আয়ের করদাতাদের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
আলোচনায় আছে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি। কিন্তু সেই বরাদ্দ কতটা কার্যকরভাবে পৌঁছাবে প্রান্তিক মানুষের হাতে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সামান্য ভাতা বাড়ানো বা কিছু কর্মসূচি চালু রাখাই যথেষ্ট নয়—দরকার গুণগত মান বৃদ্ধি, যাতে সেই সুরক্ষা বাস্তব অর্থেই জীবন রক্ষাকারী হয়।
শেয়ারবাজার, ব্যাংক খাত ও রপ্তানিতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার কতটা অগ্রসর হয়েছে তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। শেয়ারবাজারে সরকার চাইছে বড় কোম্পানিকে আইপিওর মাধ্যমে বাজারে আনতে, কিন্তু কাঠামোগত দুর্বলতা ও অনিয়ন্ত্রিত লেনদেনের সংস্কৃতি না পাল্টালে তাতে আস্থা ফেরানো কঠিন। ব্যাংক খাতের কথায় আসা যাক—অভ্যন্তরীণ ঋণের এক বিরাট অংশ এই খাতে গিয়ে ‘অসুস্থ’ হয়ে আছে। পুনর্গঠন ও অডিটের কথা বলা হলেও ফল এখনো অনিশ্চিত।
তবে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। যেমন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কিছুটা কৌশলী হয়েছে। ভর্তুকি ব্যবস্থা, বিশেষত জ্বালানি ও কৃষিতে, ঠিক রাখা হয়েছে। এনবিআরের স্বাধীনতা সীমিত করে আলাদা নীতিনির্ধারণী ইউনিট তৈরির চিন্তাভাবনাও ইতিবাচক। কালো টাকা নিয়ে বড় সুযোগ না দিয়ে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনে বাস্তবিক ভ্যালুয়েশন নির্ধারণের উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য ভালো সিগনাল।
এই বাজেট এমন এক সময়ে পেশ হচ্ছে, যখন জনগণের আস্থা, ব্যবসার গতি এবং অর্থনীতির গভীরে থাকা দুর্বল জায়গাগুলোর সংস্কার একত্রে প্রয়োজন। বাজেট যদি সত্যিই ‘সমতাভিত্তিক ও কল্যাণমুখী’ হতে চায়, তাহলে শুধু সংখ্যা নয়, মানের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নয়ন মানেই অবকাঠামো নয়—স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনাই আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত।
পরিশেষে বলা যায়, আজকের বাজেট নিছক একটি নথি নয়, এটি একটি বার্তা। সেই বার্তা হওয়া উচিত—আমরা অর্থনীতির গতি বাড়াতে চাই, বিনিয়োগে আস্থা ফিরিয়ে আনতে চাই, এবং সব শ্রেণির মানুষের জন্য একটি বাস্তব, ন্যায্য ও টেকসই বাংলাদেশ গড়তে চাই।