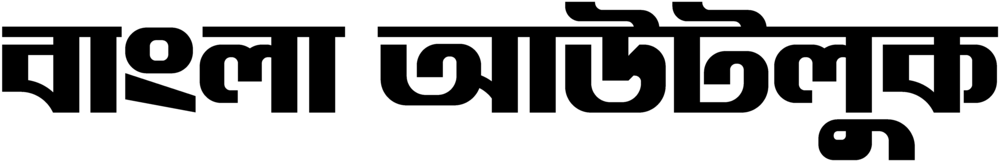ইরান থেকে আসলে কী চায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল
মুহান্নাদ আয়্যাশ
প্রকাশ: ২৪ জুন ২০২৫, ১১:০২ এএম

২০২৫ সালের ২২ জুন, তেহরানের ইংলাব স্কয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন ইরানিরা। [ছবি: আত্তা কেনারে/এএফপি]
২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে দেওয়া এক সাক্ষ্যে তৎকালীন সাবেক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে” জয় পেতে এবং ইরাক ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র না যেতে দিতে হলে ইরাকে সামরিক হস্তক্ষেপ জরুরি। তিনি দাবি করেন, যুদ্ধ খুব দ্রুত শেষ হবে এবং শুধু ইরাক নয়, পুরো অঞ্চলে পশ্চিমা-পন্থী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে, এমনকি ইরানেও। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো হয়।
ইরাক যুদ্ধ শুরুর আগেই অনেকে জানতেন, সাদ্দাম হোসেনের শাসন গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করছিল না, এবং তার সঙ্গে আল-কায়েদার কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং এই যুদ্ধ যে ধ্বংস, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও শাসনব্যবস্থার ভেঙে পড়া ডেকে আনবে তা অনেকেই আগেই বলেছিলেন। আজকের ইরাক একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্র, যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট প্রকট।
এখন যখন ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, অনেক বিশ্লেষক বলছেন, তারা আবারও ইরাক যুদ্ধের সেই ভুল পথেই হাঁটছে। তবে এই মন্তব্যগুলো সঠিক হতো যদি ইরাক আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রতিরোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতো। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মূল লক্ষ্য ছিল ইরাককে এমন এক রাষ্ট্রে পরিণত করা, যে আর ইসরায়েলের বসতি সম্প্রসারণবাদী প্রকল্প বা মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। একই উদ্দেশ্য আজ ইরানকেও লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে।
ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মতোই, ইরান ‘পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারপ্রান্তে’— এমন দাবি ভিত্তিহীন। কোনো প্রমাণ দেখানো হয়নি যে ইরান সত্যিই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। বরং বিপরীতভাবে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল নিজেরাই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ— একটি তো ইতিহাসে একমাত্র রাষ্ট্র যারা দুইবার পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করেছে এবং অন্যটি এখনো পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে সই করেনি।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আসলে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে নয়, ইরানকে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দেখতেই ভয় পায়। তাই তারা সরাসরি “শাসন পরিবর্তনের” দাবি তুলছে। নেতানিয়াহু, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম ও টেড ক্রুজ এই দাবিতে একাত্ম হয়েছেন। এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে শাসন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন।
তারা দাবি করছেন, ইরানি জনগণ যেন ‘স্বাধীনতার জন্য দাঁড়ায়’। অথচ বাস্তবে তারা এমন একটি শাসনব্যবস্থা চায়, যা ১৯৭৯ সালের আগে পাহলাভি রাজতন্ত্রের মতো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কথা শুনবে।
ইরাকের মতো ইরানকেও যদি দুর্বল, বিভক্ত ও গৃহযুদ্ধ-পীড়িত করে তোলা যায়, তাহলে তা ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আসে। ১৯৯০-এর দশক থেকে এই নীতি তাদের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ১৯৯৬ সালে রিচার্ড পার্লসহ কয়েকজন মার্কিন নীতিনির্ধারক একটি নথি তৈরি করেন— “A Clean Break”— যেখানে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ঠেকানোর নামে যেসব হামলা চালানো হবে, তা আসলে ইসরায়েলের কৌশলগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।
ইরাকে যুদ্ধের পর যেভাবে আইএস ও অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, একই রকম জটিলতা ইরানে দেখা দিতে পারে। এমনকি এই যুদ্ধ পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের হুমকিও বাড়াচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশ এখন বুঝতে পারছে, নিজেদের রক্ষা করতে হলে পারমাণবিক অস্ত্রের দিকেই ঝুঁকতে হবে।
ইসরায়েল চায় পুরো অঞ্চল তাদের সামনে নতজানু হোক। তারা মনে করে, ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই তারা নিরাপদ থাকবে। এজন্য তারা যুদ্ধ, ধ্বংস ও অস্থিরতাকে ব্যবহার করছে। এর জন্য তাদের কোনও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দায় বহন করতে হয় না।
যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক। তা জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে এবং চীনকে প্রতিহত করার মার্কিন পরিকল্পনায় বড় বাধা হতে পারে।
২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ যেমন সারা বিশ্বের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলেছিল, তেমনই এবারও যুদ্ধের পরিণতি শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, বিশ্বজুড়েই ভয়াবহ হবে। অথচ এবার এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর প্রতিক্রিয়া আরও নিস্পৃহ।
যদি বিশ্ব সত্যিই শান্তি ও স্থিতি চায়, তাহলে এই ঔপনিবেশিক সহিংসতা ও সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানানো দরকার। ইসরায়েলকে বসতি প্রকল্প বন্ধ করতে বাধ্য করতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে হবে।
এই একমাত্র পথ যা অঞ্চলটিকে চিরস্থায়ী অস্থিরতা, মানবিক দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।